- 14 October, 2025
- 0 Comment(s)
- 409 view(s)
- লিখেছেন : অমর্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রত্যাশা মতোই ভারতে ফ্যাসিবাদ ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। সেই বিস্তারের চলনও পূর্বাভাস-মতোই। এখনও যে, কোনো কোনো বামপন্থী দলের ভিতরেও কেন্দ্রীয় শাসক দলকে সম্পূর্ণ-ফ্যাসিস্ত অভিধায় সংজ্ঞায়িত করা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে, সেইটিই বরং আশ্চর্যের ও আশঙ্কার। তবু ফ্যাসিবাদের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক নিয়মে সেই বিস্তৃতির প্রতিক্রিয়ায় নানাবিধ সামাজিক ঘটনা-পরম্পরারও সৃষ্টি হচ্ছে। সকল সময়ে তা যে সার্থক শ্রেণীসংগ্রাম – অনেক বড় কথা হয়ে গেল বোধহয় – হয়ে উঠতে পারছে তা একেবারেই নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে তেমন সমস্ত ঘটনার উদ্ভাবন ঘটছে। নগ্ন ফ্যাসিবাদের উত্থানে, মধ্যপন্থী বুর্জোয়া বা আধা-বুর্জোয়া সম্প্রদায় যে অনেক সময়েই পারিপার্শ্বিক অবস্থা অবলোকন করে, এতদিন সুবিধা ভোগ করে আসা ডুবন্ত নৌকো ছেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার কাটতে চেষ্টা করে – এ যেন তারই বাস্তব উদাহরণ। তবু, শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটুকুই ধার করে নিয়ে বলতে চাইব, ফ্যাসিবিরোধিতার ভানটুকুও ভালো বোধহয়। ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে সকলের চৈতন্য হোক।
যে প্রসঙ্গে এমন নান্দীমুখ – বিগত বেশ কিছু মাস যাবৎ কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপি ও বৃহত্তর সংঘ পরিবারের তরফে বাংলা ভাষা, বাংলাভাষী নাগরিক সম্প্রদায়, তদুপরি বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, রীতিমতো পরিকল্পিত ভাবে লাগাতার সংঘবদ্ধ আক্রমণের এক দেশব্যাপী প্রভাব দেখা যাচ্ছিল। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বৃহত্তর বাঙালি সম্প্রদায় যেন প্রতিবাদ-মঞ্চ হিসেবে বিশেষ ভাবে বেছে নিয়েছিল শারদোৎসব উদযাপনের সময়। রাজ্য সরকারের একাধিক পদক্ষেপ এই শারদোৎসব প্রসঙ্গে সমর্থন না করলেও, তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়, এবং পাশাপাশি একাধিক সামাজিক-রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উৎসাহে, হঠাৎই যেন শারদোৎসবের মঞ্চ হয়ে উঠল আরও সবিশেষ ভাবে বাঙালিত্ব উদযাপনের মুক্তাঙ্গন। আমরা দেখলাম শারদোৎসবের মণ্ডপসজ্জায় উঠে আসছেন লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, সমরেশ বসু, ঋত্বিক ঘটক, বাদল সরকারের মতো মণীষীরা। সম্মানিত হচ্ছে তাঁদের সৃষ্টি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই উদযাপিত হচ্ছে, বাঙালি হয়েও (নাকি বলব বাঙালি হয়েই?) তাঁদের চিরকালের, আজীবনের প্রগতিশীল, আন্তর্জাতিক, শ্রেণিসচেতন, প্রতিষ্ঠানবিরোধী ভাবনা, চিন্তা, ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় মনোবৃত্তির প্রকাশ।
এমন এক সময়েই তাই, আরও মনে হল – বাঙালি নারীর বিশ্ববিজয়ের বিষয়েও নতুন করে কিছু লেখা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে দেশবিদেশের নারী বৈজ্ঞানিকদের বিষয়ে বেশ কিছু ধারাবাহিক নিবন্ধ রচনার সৌভাগ্য হয়েছিল। পেশাগত ভাবে বিজ্ঞান-বিষয়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ জড়িয়ে থাকার কারণে, সেসময়ে সেই ধারাবাহিক রচনার দুঃসাহস দেখিয়েছিলাম। বেশ কিছু বছর কেটে গেলেও, এখনও নিবন্ধগুলির সমাদর দেখে, এই প্রসঙ্গে মনে হল হঠাৎ - আলাদা করে সেই তালিকার বাঙালিনীদের এই বিশেষ সময়ে, একপাশে একটু সরিয়ে এনে দেখলেও তো হয়! যে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতারই আমরা যেমন বিরোধী, তেমনই কোনো কোনো ক্ষেত্রে নগ্ন সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করার সম্মানজনক কোনো প্রচেষ্টাকেও কখনও ভুল বলে মনে হয়নি। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের যেমন কোনো ভাষাগত সীমাবদ্ধতা নেই, লিঙ্গগত প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিন্যাস নেই – তবু, একমুখী ফ্যাসিবাদের নগ্ন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির বিশ্বজনীনতা, বাঙালি নারীর মেধাগত উৎকর্ষের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি, এই বিষয়গুলিকেও স্মরণ করার পিছনে আজ কোনো অন্যায় দেখি না। বরং মাতৃরূপেণ, শক্তিরূপেণ, সৃষ্টিরূপেণ’র পাশাপাশি বুদ্ধিরূপেণ নারীপ্রতিমাকেই আজ সবিশেষে স্মরণ করতে ইচ্ছে হয়। সেই ভাবনা থেকেই এই নিবন্ধের সূত্রপাত।
উপনিষদের সেই যুগ। গার্গী-অপালা-মৈত্রেয়ীর পাশাপাশি খনার কথাও লিখেছিলাম। যদিও খনা-প্রসঙ্গে প্রক্ষিপ্ত তথ্যের সমাহার এতই বিচিত্র, ও সেই সমস্ত তথ্যের সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণও এত কম, খনা-র বাঙালিত্বের বিষয়ে জোর দিয়ে কিছু বলা চলে না। তবু তাঁর কর্মক্ষেত্র যে এই বাংলার মাটিতেই কোথাও, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ নিশ্চিত হওয়া চলে। পাশাপাশি, বহুবছরের বিকৃতির কারণে খনা’র বচনগুলি ক্রমশ বিজ্ঞানের ব্যাপ্তিকে দূরে সরিয়ে রেখে জ্যোতিষশাস্ত্রের চরম সংকীর্ণতার কাছাকাছি সরে গিয়েছে। তাই দুর্ভাগ্যবশত আজকের আধুনিক ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে অন্ধ সনাতনী মনোভাবের চরম দাপটের কারণে, খনার অবদান হিসেবে সেই বিষয় বা বচনগুলি স্মরণ করাও কিঞ্চিৎ বিপজ্জনক। অথবা অতথ্য-উদ্রেককারী বোধ হয়। তবুও বলব বাংলার মাটিতে খনা’র কীর্তিকলাপ অথবা তাঁর সম্পর্কিত সমস্ত গল্প-কাহিনি-আলোচনা, হয়তো এটাই প্রমাণ করে ইতিহাসের আগের সে যুগেও বাঙালি নারীর মেধা ও বৈজ্ঞানিক সত্তার বিকাশ অনেকটাই সম্ভব হয়েছিল। এরপর কেটেছে সহস্র বছর। আমরা বেশ কিছু সময় পেরিয়ে আধুনিক পৃথিবীতে এসে দাঁড়াই।
২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮ – জনৈকা ইংরেজ ভদ্রমহিলা তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখছেন, “আমাকে মিসেস গাঙ্গুলীর সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানাতে পারো কি? যতদূর শুনেছি তিনি ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম মহিলা প্র্যাকটিসিং ফিজিশিয়ান হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছেন, এবং আগামী বছর মার্চ মাসে তিনি শল্যচিকিৎসার অন্তিম পরীক্ষাতেও অংশ নিতে চলেছেন। তিনি অন্ততপক্ষে একটি বা দুটি সন্তানেরও জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু যতদূর জেনেছি, সেই সময়ও মাত্র ১৩ দিনের বিরতির পরই তিনি ফের চিকিৎসক হিসেবে তাঁর কাজে যোগদান করেছিলেন। ... আমি এই প্রসঙ্গে লেডি ডাফরিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছি, কলকাতার কোনও একটি হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডে যদি মিসেস গাঙ্গুলীকে চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ করা যায় ...” জনৈকা এই ইংরেজ ভদ্রমহিলার নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল; আর পত্রে উল্লিখিত মিসেস গাঙ্গুলীর সম্পূর্ণ পরিচয় কাদম্বিনী গাঙ্গুলী - সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকে ধরলে, যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রথম স্বীকৃত মহিলা প্র্যাকটিসিং ফিজিশিয়ান। কাদম্বিনী জন্মেছিলেন বিহারের ভাগলপুরে বিশিষ্ট এক ব্রাহ্ম পরিবারে। তাঁর পিতা ব্রজকিশোর বসু ছিলেন একজন সমাজসংস্কারক, এবং স্থানীয় স্কুলের প্রধানশিক্ষক। ১৮৬৩ সালে তিনি এবং অভয়চরণ মল্লিক ভাগলপুর মহিলা সমিতি’র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সমিতিই সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্বীকৃত মহিলা সমিতি বলে পরিচিত। কাদম্বিনীর বিয়ে হয় তাঁর চেয়ে সতেরো বছরের বড় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। কিন্তু আলোকপ্রাপ্ত এবং শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে, প্রথমে পিতা ব্রজকিশোর এবং পরবর্তীতে স্বামী দ্বারকানাথ দুজনেই কাদম্বিনীর শিক্ষা এবং গুণগত সমৃদ্ধির বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন।
সমাজের সমস্ত বাধাবিপত্তি কুসংস্কারকে তুচ্ছ করে কাদম্বিনী উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত রওয়ানা হন। ২৩ মার্চ, ১৮৯৩ – কাদম্বিনী লন্ডনে এসে পৌঁছন। এরপর একে একে তিনি এল. আর. সি. পি. (এডিনবার্গ), এল. আর. সি. এস. (গ্লাসগো), এবং জি. এফ. পি. এস. (ডাবলিন) এই তিনটি ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি নেপালে যান এবং সেদেশের রাজা দেব শমশের জং বাহাদুর রানা’র মায়ের চিকিৎসাভার গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি কেবল নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি বা নিজের জীবনে উন্নতিই নয়, সমাজের সার্বিক পরিবর্তনের প্রয়োজনেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৮৫তে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় সেই সময় কোনও মহিলাকে কংগ্রেসের সদস্যপদ দেওয়া হতো না। ১৮৮৯ সালে প্রথমবারের জন্য আরও চারজন মহিলার সঙ্গে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং কংগ্রেসের ইতিহাসে প্রথম মহিলা হিসেবে পরের বছর, ১৮৯০ সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি ভাষণ দেন। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে তিনি কলকাতায় একটি মহিলা সমাবেশের আয়োজন করেন। ১৯১৪ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর কলকাতা সফরকালে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সম্মানার্থে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিল, ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী তাতে সভাপতিত্ব করেন। স্বামী দ্বারকানাথের সঙ্গে তিনি আসামের চা-শ্রমিকদের দুর্দশার বিষয়টিকেও জনসমক্ষে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা চালান। ১৯২২এ সরকারি কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি কবি কামিনী রায়ের সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যার কোলিয়ারি অঞ্চলে সেখানকার মহিলা শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করেন।
কাদম্বিনী প্রসঙ্গে এমন বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন ছিল। সে যুগের অগ্রণী নারীদের মধ্যে তিনি প্রথম। গোটা দক্ষিণ এশিয়ার নিরিখে তিনিই প্রথম স্বীকৃত মহিলা প্র্যাকটিসিং ফিজিশিয়ান! এবং তিনি বাঙালিও বটে। প্রাদেশিক না হয়েও গর্ব অনুভব করতে ইচ্ছে হয়। কাদম্বিনীর সঙ্গে সঙ্গেই আরও এক নাম মনে আসে। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এবং চন্দ্রমুখী বসু, দুই বাঙালিনীই প্রথম মেয়েদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট হবার সম্মান অর্জন করেন। ১৮৮২তে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী উভয়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ-স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যদিও পরবর্তীতে, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের পথে তাঁদের মধ্যে অবশ্য একমাত্র কাদম্বিনীই এগিয়েছিলেন। তবু বিজ্ঞানমঞ্চে বাঙালি নারীর জয়যাত্রার কেবলই সূচনাক্ষণ তখন।
১৯৩৬। বেয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হতে তখনও বাকি ছয় বছর। কলকাতার রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে সেই বছর, একমাত্র মহিলা পরীক্ষার্থী হিসেবে এমএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বিভা চৌধুরী। এরপর ১৯৩৯এ তিনি গবেষক হিসেবে বোস ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে, বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসুর অধীনে গবেষণা শুরু করেন। তাঁদেরই যুগ্ম গবেষণায় সম্ভব হয় মেসন-কণার আবিষ্কার! সেই সময় প্রথমে দার্জিলিংয়ে ও পরে সান্দাকফু পাহাড়ে বিভা চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে শুরু হয় মহাজাগতিক তরঙ্গে মেসন-কণার উপস্থিতি নির্ণয়ের কাজ। ১৯৪১, রবীন্দ্রপ্রয়াণের বছর। সেই বছরেই বিশ্বখ্যাত নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় দেবেন্দ্রমোহন বসু ও বিভা চৌধুরীর যৌথ প্রচেষ্টায় লিখিত গবেষণাপত্র, ‘আলোকচিত্রের মাধ্যমে মেসোট্রন কণার ভর-নির্ণয়’। এখানেই শেষ নয়। এই গবেষণা-পরবর্তীতে বিভা চৌধুরী পিএইচডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বখ্যাত পদার্থবিদ প্যাট্রিক ব্লেকেটের অধীনে ছাত্রী হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৯ সালে সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বিভাদেবী পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি উপাধি লাভ করেন। অনেকে মনে করেন, প্যাট্রিক ব্লেকেট পরবর্তীতে যখন নোবেল সম্মানে ভূষিত হন – তৎকালে, সেই সম্পর্কিত গবেষণার সঙ্গেও বিভা চৌধুরী প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে দেশে ফিরে এসে, শ্রীমতি বিভা চৌধুরী টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগদান করেন। কে-মেসন কণার আবিষ্কার-সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে। এরপর ১৯৫৪ সালে অতিথি-গবেষক হিসেবে তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। সবশেষে আবারও দেশে ফেরার পর, প্রথমে ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি ও পরবর্তীতে কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়র ফিজিক্স, এই দুই প্রতিষ্ঠানে শ্রীমতি চৌধুরী সম্মানের সঙ্গে তাঁর গবেষক-জীবন অতিবাহিত করেন।
আবারও পিছিয়ে যাই। ১৯৪৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও জারি রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা গবেষক হিসেবে পিএইচডি উপাধি লাভ করেন অসীমা চট্টোপাধ্যায়। উদ্ভিজ-পদার্থের বিভিন্ন রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ও জৈবরাসায়নিক সংশ্লেষের ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারিক গুরুত্ব, এই সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর গবেষণায় তিনি পথ-প্রদর্শক হিসেবে স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরামর্শ-সান্নিধ্য লাভ করেন। এরপর প্রথমে আমেরিকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎপরবর্তীতে সেদেশেরই ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, ক্যালিফোর্ণিয়ায় তিনি পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণার সুযোগ পান। এরপর দেশে ফিরে এসে অসীমা চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। মৃগীরোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশেষ এক ওষুধ তৈরির সময়, তাঁর গবেষণা বিশেষ অবদান রাখে। এছাড়াও কর্কট রোগ নিরাময়ের প্রসঙ্গেও একাধিক ওষুধ ও রাসায়নিকের উপযোগিতা নির্ণয়ে অধ্যাপক অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা কার্যকরী হয়। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত তাঁর গবেষক জীবনে, তাঁর দ্বারা সংশ্লেষিত একাধিক ওষুধ, আজও মৃগীরোগের চিকিৎসা, এমনকি কেমোথেরাপির সময় ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর শরীরেও ব্যবহার করা হয়। তাঁর হাত ধরেই লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে রসায়ন বিভাগের পথচলার সূত্রপাত। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি-প্রাপক ও পরবর্তীতে খয়রা-অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের জন্য তিনি শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরষ্কার ও ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক পুরষ্কার পদ্মভূষণ সম্মানেও সম্মানিত হন।
প্রথম মহিলা হিসেবে স্বাধীনতার আগেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন অসীমা চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর বিষয় ছিল রসায়ন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা হিসেবে পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি ডিগ্রি লাভের কৃতিত্ব অর্জন করতে পূর্ণিমা সিংহের সময় লেগেছিল আরও দশ বছর। ১৯৫৬-৫৭ সালে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অধীনে গবেষণার ফলস্বরূপ পূর্ণিমাদেবী ফিজিক্সে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। এই সময় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির ব্যবহারিক অনুসন্ধান। এই কাজের প্রয়োজনে বিশ্বযুদ্ধের পর কলকাতার খোলা বাজারে বিক্রি হওয়া নানাবিধ লোহা-লক্কড়ের পুরনো জিনিস, যন্ত্রপাতি – ইত্যাদি ঘেঁটে পূর্ণিমাদেবী তাঁর গবেষণার জন্য দরকারি সমস্ত সূচক-নির্ণায়ক, পরিমাপক-যন্ত্র ইত্যাদি জোগাড় করেন। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা যখন শিল্প-সংস্থা ও শিক্ষাঙ্গনের যৌথ পরিকল্পনা বা ইণ্ডাস্ট্রি-এ্যাকাডেমিয়া কোল্যাবোরেশনের কথা বলি, তখন সেই যুগেই আসাম অয়েল কোম্পানির সঙ্গে যৌথ ভাবে পূর্ণিমা সিংহ তাঁর গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। পরবর্তীতে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘অরিজিন অব লাইফ’ প্রকল্পেও তিনি গবেষণা করেন। বিজ্ঞানচর্চার ভারী গবেষণার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও সঙ্গীত-বিষয়েও পূর্ণিমা সিংহের আগ্রহ ছিল। সহজ বাংলায় বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবনের উপর তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও সহজ বাংলায় তিনি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আরুইন শ্রডিঙ্গারের ‘মাইণ্ড এ্যান ম্যাটার’ বইটি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য অনুবাদ করেন। পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে তবলা ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম নেওয়া পূর্ণিমা পরবর্তী জীবনে পদার্থবিদ্যার পাশাপাশি নৃতত্ত্ব, জনজাতি ও লোকায়ত সঙ্গীতের বিষয়েও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ২০০৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় আন্দামানের জারোয়া জনজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গীতচর্চার বিষয়ে তাঁর একটি দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরপর ইলা মজুমদার।
বিভা চৌধুরী, অসীমা চট্টোপাধ্যায়, ও পূর্ণিমা সিংহের জন্ম যথাক্রমে ১৯১৩, ১৯১৭ ও ১৯২৭এর বিভিন্ন সময়। শিবপুর বিই কলেজের প্রথম মহিলা মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়র ইলাদেবী কালানুক্রমে এঁদের সকলের পর ১৯৩০এ জন্মগ্রহণ করেন। যে বছর তিনি শিবপুরের কলেজে ভর্তি হন, সেই শিক্ষাবর্ষেই তাঁর সঙ্গে আরও এক মহিলা সেই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। তবু সেশন শুরুর এক বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় জন কলেজ ছেড়ে যান। শেষ অবধি ১৯৫১ সালে শিবপুর বিই কলেজের ইতিহাসে প্রথম মহিলা হিসেবে স্নাতক হন ইলা মজুমদার। স্নাতকোত্তর-পাঠের সময় ইলা দেবী ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরে ঐতিহ্যবাহী বার এ্যাণ্ড স্ট্রাউড সংস্থায় গবেষক হিসেবে কাজ করেন। এরপর দেশে ফিরে কিছুকাল দেহরাদুনের অর্ডন্যান্স কারখানায় চাকরির পর দিল্লির সরকারি পলিটেকনিক কলেজে তিনি অধ্যাপনার দায়িত্ব নেন। তখন ১৯৫৫ সাল। এরপর কলকাতায় ফিরবেন ইলা মজুমদার। ইনস্টিটিউট অব জুট টেকনোলজিতে অধ্যাপনা করবেন। কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে এসে গড়িয়াহাটের উইমেনস পলিটেকনিক কলেজের অধ্যক্ষা হিসেবে তিনি দায়িত্ব সামলাবেন। এছাড়াও ১৯৮৫তে ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে বাংলাদেশে মহিলা পলিটেকনিক গড়ে তোলার বিষয়েও বিশেষ পরামর্শদাতা হিসেবে ইলাদেবী কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন।
… কাজেই বাঙালিকে, বাঙালি নারীকে, অপদস্থ করার, হেনস্থা করার, কুৎসা রটিয়ে হীন প্রতিপন্ন করার যে চক্রান্ত আরএসএস-সংঘের দালাল, কুচক্রীরা করে থাকেন, তাদের জবাব দেওয়ারও কোনো দায় নেই আমার। এই লেখা শেষ করছি যখন, আন্তর্জাল মাধ্যমে ঠিক তখনই খবর ভেসে আসছে দেখতে পাই, নয়াদিল্লিতে তালিব বিদেশমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে “বিশেষ অনুরোধবশত” কোনো মহিলা সাংবাদিককে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অচ্ছে দিনের ভারতবর্ষে আজ সংঘ-পরিবারের অঙ্গুলিহেলনে চলা ভারত সরকারের স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে উঠে আসছে আফগানিস্থানের তালিব-সরকারের নাম! মেধা, প্রগতিশীলতা, নারী-অধিকার – এই সমস্ত বিষয়ে সংঘ তথা কেন্দ্রের কোনো মতামতকেই তাই আজ, আর কোনো গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন দেখিনা। নিজ কর্মক্ষেত্রে দেখেছি, কীভাবে আজও বিজ্ঞান-গবেষণা থেকে শুরু করে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে বাঙালি তথা বাঙালি নারীর মেধা ও মণীষার জয়রথ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রাদেশিক না হয়েই বলছি, গো-বলয়ের ভক্তকুলের তরফে আমাদের কোনোদিন কোনো বিশেষ শংসাপত্রের প্রয়োজন পড়বে না। ইতিহাসে অসীমা চট্টোপাধ্যায়, বিভা চৌধুরী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী অথবা ইলা মজুমদারদের মতো একেকজনেরই নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। অপরপক্ষে, গোলওয়ালকর থেকে মোল্লা উমর অথবা মোদী থেকে খোমেইনি-তুল্য একেকজনের জন্য বরাদ্দ থাকবে একরাশ ঘৃণিত তথ্যের বিবরণ, পৃথিবীর ইতিহাসকে তাঁরা উলটো পথে পাঠাতে চেয়েছিলেন।
.jpg)

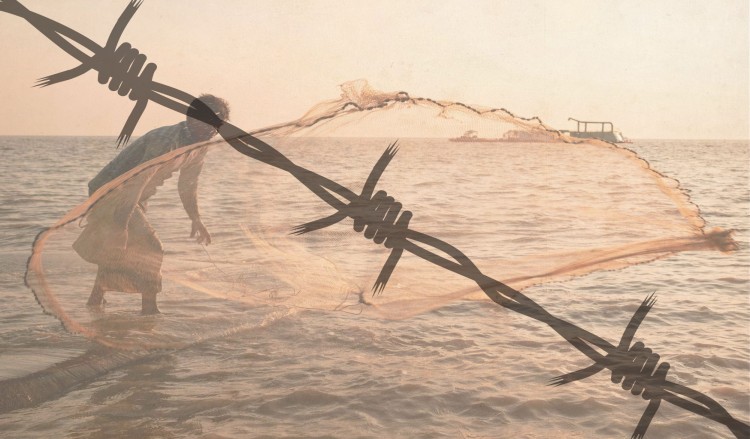


0 Comments
Post Comment