- 09 December, 2022
- 0 Comment(s)
- 2133 view(s)
- লিখেছেন : আফরোজা খাতুন
১৮৮০ সালে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক রক্ষণশীল অভিজাত জমিদার বাড়িতে রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রয়াণ মাত্র ৫২ বছর বয়সে ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর, কলকাতায়। জন্মও ৯ ডিসেম্বর বলে অনেকে উল্লেখ করলেও তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে এখনও বিতর্ক রয়েছে। যদিও বাংলাদেশ সরকার ৯ ডিসেম্বরকে জন্ম তারিখ ধরেই রোকেয়ার জন্ম শতবর্ষ পালন করেছে। অনেকেই তাঁকে বেগম রোকেয়া রূপে চেনেন। তবে উল্লেখ্য ‘বেগম’ শব্দটি কখনোই তিনি ব্যবহার করেননি। ছোটবেলার নাম রোকেয়া বা রুকাইয়া খাতুন। বিয়ের পর তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বা মিসেস আর. এস. হোসেন নামে পরিচিত হলেন।
রোকেয়া বড় হয়েছেন কঠোর অবরোধ প্রথার মধ্যে। মেয়েদের প্রথাগত লেখাপড়ার কোনো সুযোগই ছিল না সেখানে। তাই কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি। গোপনে বাড়িতেই দাদা ইব্রাহিম সাবের আর দিদি করিমুন্নেসার কাছে ইংরেজি, বাংলা শেখেন। দিনের আলোয় পড়ার সুযোগ ছিল না। রাত্রিতে বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর দাদা ইব্রাহিম সাবেরের কাছে লুকিয়ে পড়াশোনা করতেন রোকেয়া। বিয়ের পর ইংরেজি-বাংলা-উর্দু বই পড়া ও সাহিত্যচর্চা শুরু। ১৮৯৬ সালে, ষোল বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয় ৩৮ বছর বয়স্ক ভাগলপুরবাসী বিপত্নীক সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। ১৯০৯ সালে সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু হয়। রোকেয়া দুটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু একটি পাঁচমাস বয়সে আর একটি চারমাস বয়সে মারা যায়। ব্যক্তিগত বিষণ্ণতা ও যন্ত্রণায় হতাশ হলেন না রোকেয়া। আত্মনিয়োগ করলেন মুসলিম মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে, সমাজসংস্কারে।
নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়ার প্রধান পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর নারীশিক্ষানুরাগী বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন আজীবন। বিশ শতকের দ্বিতীয় বছরে বাংলা সাহিত্যে রোকেয়ার আর্বিভাব ‘পিপাসা’ (মহরম।) প্রবন্ধ লিখে।
যখন যেদিকে চাই,কেবলি দেখিতে পাই-
“পিপাসা, পিপাসা” লেখা জ্বলন্ত ভাষায়
শ্রবণে কে যেন ঐ “পিপাসা” বাজায়।
বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই সমাজ প্রগতির উদ্দেশ্যে তিনি নারী শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হন। সাহিত্যচর্চার মধ্যেও রোকেয়া পালন করেন সমাজ সংস্কারের ভূমিকা। নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন নারীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে। অংশ নেন নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে।
নারীবাদী আন্দোলনের ধারায় রোকেয়া
উনিশ শতকের বাংলায় নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের ফলে। সব দেশের সমাজের মূলস্রোত থেকে নারীরা বিচ্ছিন্ন, তারা প্রান্তিকায়িত অপর। তাই নারীবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনে। পাশ্চাত্যে নারী স্বাধীনতার সূচনা মুহূর্তে নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের শুরু থেকে ক্রমশ বেড়ে যায় মেয়েদের অধিকার বিষয়ে সামাজিক চেতনা। এই সময় ইংল্যান্ডে এগিয়ে আসেন Mary Wollestonecraft, Caroline Norton, William Thompson, J.S Mill প্রমুখ নারী, পুরুষগণ। ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণায় উজ্জীবিত Mary Wollestonecraft (১৭৫৯-১৭৯৭)-এর ‘Vindication of the rights of Women’ (১৭৯২) গ্রন্থে বলেছেন, নারী ও পুরুষের যুক্তি, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে তার পরিবেশ অনুযায়ী। প্রতিকুল পরিবেশের জন্যই নারীর হীনমন্যতা তৈরি হয়। নারী-পুরুষ সমবন্ধুত্বভাবাপন্ন হোক এটা তিনি চেয়েছিলেন। আর সেটা সম্ভব শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে। দার্শনিক J.S Mill (১৮০৬-১৮৭৩) তাঁর ‘The Subjection of Women’ (১৮৬৯) গ্রন্থে নারী-পুরুষের সামাজিক সম-অধিকারের কথা যুক্তিশীলতার সঙ্গে উপস্থিত করেন। পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলন ও তাঁদের বইপত্র সেই সময়ের বাংলার শিক্ষিত সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবেও এদেশের নারীর অবস্থানকেই নির্দেশ করা হয়েছিল। শিক্ষিত সমাজের একাংশের মধ্যে নতুন এক চেতনার উন্মেষ ঘটে। হিন্দু সমাজের মেয়েদের অবস্থান নিয়ে চিন্তিত হন তাঁরা। চিন্তাশীল সংস্কারকগণের কর্মসূচিতে ছিল নারীর জন্য ন্যায়সঙ্গত স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা। রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নারীদের অধিকারের জন্য লড়াইয়ের প্রথম সাফল্য ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রোধ আইন। অপরদিকে উনিশ শতকের সামাজিক চেতনার প্রতিফলন হিসেবেও গুরুত্ব পায় স্ত্রীশিক্ষা।
সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কের ধারণা পাল্টাতে শুরু করে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে। যদিও একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যেই নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ এল। প্রথমে তাঁদের শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য ছিল গৃহ সামলানোয় নিপুণ করে তোলা। আর স্বামীর যোগ্য সঙ্গিনী হয়ে ওঠা। তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙালি নারীদের আত্মপ্রকাশের স্বতন্ত্র একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। সেই পরিবেশের ধারায় পরবর্তীতে রোকেয়া তুলেছিলেন পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারের প্রশ্ন। যোগ্য সহধর্মিণী হওয়াকে নারীদের বৃহত্তম লক্ষ্য বলে তিনি মনে করেননি। অবরোধের পীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে দেশের সুনাগরিক হওয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনতা নির্ভর করে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ওপর এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন। এই বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার তাগিদে সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা প্রতিরোধ করে আপন লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন রোকেয়া।
১৯০৩-এ তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ ‘অলঙ্কার না Badge of Slavery?’—নারীবাদী ভাবনার প্রথম প্রকাশ পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে। এই প্রবন্ধটি বিতর্কের সঞ্চার করে পুরুষ ও নারীর মধ্যেও। তাই সংশোধিত আকারে ‘আমাদের অবনতি’ শিরোনামে প্রকাশ হয়। তবুও তীব্র প্রতিবাদ চলে এই প্রবন্ধ নিয়ে। আর এক দফা সংশোধন করে ‘স্ত্রী জাতির অবনতি’ শিরোনামে মতিচুর সংকলনে প্রকাশিত হয়। নারীদের সৌন্দর্য সম্পর্কে পুরুষদের তৈরি মিথ যে নারীদেরকেই দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলে, তা বুঝতে পেরেছিলেন রোকেয়া। এই পুরুষতান্ত্রিক কৌশলের কথা রোকেয়া জানতেন বলেই লিখলেন— “আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি—এগুলি (badges of slavery)। ঐ দেখ কারাগারে বন্দীগণ লৌহনির্ম্মিত বেড়ী পায়ে পরিয়াছে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ “মল” পরিয়াছি।” উহাদের হাতকড়ী লৌহ নির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত “চুড়ি।” বলাবাহুল্য অনেকে এক হাতে লোহার ‘বালা’ও পরেন। কুকুরের গলে যে dog-collar দেখি, উহারই অনুকরণে আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে! অশ্বহস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণশৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া বলি “হার পরিয়াছি।” গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া ‘নাকা দড়ী’ পরান, আমাদের স্বামী আমাদের নাকে নোলক পরাইয়াছেন। অতএব দেখিলে ভগিনী আমাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি badges of slavery ব্যতীত আর কিছু নহে। আবার মজা দেখ, যাঁহার শরীরে badges of slavery যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যাগণ্যা!... দরিদ্র কামিনীগণ স্বর্ণরৌপ্যের হাতকড়ী না পাইয়া কাচের চুড়ি পরিয়া দাসীজীবন সার্থক করে। যে বিধবা চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে, তাহার মতো হতভাগিনী এ জগতে নাই!! অভ্যাসের কি অপার মহিমা। দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচক গহনা ভাল লাগে।’ রোকেয়া বলেছেন গয়না পরে মেয়েদের কোন উন্নতি হয় না। ওটা শুধু টাকার শ্রাদ্ধ। স্বর্ণ মুক্তার অলঙ্কারে মেয়েকে সাজিয়ে না তুলে ঐ টাকা দিয়ে বই কিনে দিলে তারা জ্ঞানগর্ভে অলঙ্কৃত হতে পারবে। ‘একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না।’
নারী জাগরণের কর্মী ও প্রেরণাদাতা রোকেয়া প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মেয়েদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার মূল কারণগুলি লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে— ‘...আমাদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে “ঈশ্বরের আদেশপত্র” বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্মের নিগূঢ মর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমার আলোচ্য নহে— ধর্মে যে সামাজিক আইনকানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্মিকগণ নিশ্চিন্ত থাকুন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর প্রেরিত দূত কিংবা দেবতা বলিয়া প্রকাশ করিয়া অসভ্য বর্বরদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি বিবেচনা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই রূপ পয়গম্বরদিগকে (ঈশ্বর প্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়। একবার সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতাটি সংস্কৃত ভাষায় সনাতন ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিলেন। তাই হিন্দু রমণীকে শিক্ষা দিলেন,--
“স্বামী বনিতার পতি, বনিতার গতি
স্বামী বনিতার যে বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনে অন্য জন,
কভু নহে সুখ মোক্ষদাতা।।”
আর হতভাগী মূর্খ নারী তাই মানিয়া লইল।
ক্রমে জগতের বুদ্ধি বেশী হওয়ায় সুচতুর প্রতিভাশালী পুরুষ দেখিলেন যে, ‘পয়গম্বর’ বলিলে আর লোকে বিশ্বাস করে না। তখন মহাত্মা ঈশা আপনাকে দেবতার অংশবিশেষ (ঈশ্বরপুত্র) বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঞ্জিল গ্রন্থ রচনা করিলেন। তাহাতে লেখা হইল, “নারী পুরুষের সম্পূর্ণ অধীনা...”। ...এই ধর্মশাস্ত্রগুলি পুরুষ রচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পাও, কোনো স্ত্রী মুনির বিধানে হয়তো তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতে। ধর্মগ্রন্থ সমূহ ঈশ্বর প্রেরিত বা ঈশ্বরাদিষ্ট নহে।...” ধর্ম”ই আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ হইতে দৃঢতর করিয়াছে, “ধর্মে”র দোহাই দিয়া পুরুষ রমণীর ওপর প্রভুত্ব করিতেছেন।’ তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্যে বিশ শতকের প্রথমদিকের সমাজেই শুধু আলোড়ন ওঠেনি, এই সময়ের রক্ষণশীলদের মনেও আলোড়ন ওঠে।
রোকেয়ার বক্তব্যে, বিভিন্ন লেখায় এই ক্ষোভ ফুটে উঠেছে যে, দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ হলেও ঘরে ঘরে নারীদের অবস্থা ক্রীতদাসীদের থেকেও খারাপ। সমাজের তৈরি নারীর এই দাসত্বের প্রশ্নে তিনি যথেষ্ট মর্মাহত ছিলেন। তিনি জানতেন, এই মানসিক দাসত্বের সঙ্গে জুড়ে আছে আবেগী শ্রমের (emotional labour) বিষয়টিও। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সুকৌশলে শ্রম-বিভাজন করেছে। মেয়েদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে যাবতীয় গার্হস্থ্য শ্রমকে। সেই শ্রমের কোন মূল্য নির্ধারণ হয়নি। ব্যক্তি পরিসরে আবদ্ধ রেখে, গৃহশ্রমে শোষণ করা হয় মেয়েদের। দাসত্ব থেকে মুক্তির একমাত্র পথ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। জীবনযাপনের জন্য নারীরা যেন কখনোই পুরুষের গলগ্রহ হয়ে না ওঠেন, তাঁরা যেন স্বাধীনভাবে উপার্জন করতে পারেন এটাই ছিল তাঁর মত। কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয় নারীর ক্ষমতায়ন। রোকেয়ার বক্তব্য, ‘‘আমরা যে গোলামজাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। ...যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয় তবে তাহাই করিব।... উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমরা “স্বামীর” গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না ?’’ স্বামীর গৃহে শ্রম দিয়ে, যে মেয়েরা জীবন কাটায়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সেই মেয়েদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর মনে করে না। যে শ্রমে পারশ্রমিক নেই, সেই শ্রমের মর্যাদাও নেই। তাই স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যবসার কাজে শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে উপদেশ দেন রোকেয়া।
শিক্ষাব্রতী রোকেয়া
জীবনের সকল অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত কর্মসাধনার মূল ব্রত রোকেয়া প্রয়োগ করলেন মেয়েদের শিক্ষা আন্দোলনের আঙিনায়। ১৯০৯ সাল, সাখাওয়াতের মৃত্যুর পাঁচ মাস পর ভাগলপুরের খলিফাবাগে পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে তৈরি করলেন ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’। কিন্তু পারিবারিক নানা বাধা-সংকটে তিনি ভাগলপুর ছাড়লেন ১৯১০ সালের ৩ ডিসেম্বর। ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ, ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ লেনে আটজন ছাত্রী নিয়ে আবার কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। সামান্য পুঁজি নিয়ে এতবড়ো শহরে স্কুল গড়তে গিয়ে তাঁকে নানান সমস্যায় পড়তে হয়। অনেক জায়গা বদলের পর ১৯৩২ সালে, রোকেয়ার মৃত্যুর ক’মাস আগে স্কুলটি উঠে আসে ১৬২ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে। ১৯৩৫ সালে সরকার এই স্কুলটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়। বর্তমানে এটি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল সরকারি বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত।
মুসলমান ঘরের মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে নিয়ে এসে শিক্ষাদান সে সময়ে ছিল একটা বিরাট সামাজিক সংগ্রাম। অবরোধবাসিনীদের যন্ত্রণা রোকেয়া মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন। সেই যন্ত্রণার উৎস তাঁর ব্যক্তিগত জীবন। ‘অবরোধ-বাসিনী’ প্রবন্ধে তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আক্ষেপ করে বলেছেন— মেছেনীকে পচা মাছের দুর্গন্ধ কেমন জিজ্ঞাসা করলে সে কোন উত্তর দিতে পারবে না। কারণ পচা মাছের গন্ধে সে অভ্যস্ত। সেইরকম অবরোধবাসিনীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় অবরোধে থাকতে কেমন লাগে, সেও কোন উত্তর দিতে পারবে না। এই রকম একটা সামাজিক পরিবেশ থেকে তাঁকে ছাত্রী যোগাড় করতে হয়েছে। একটি ন’বছরের মেয়ে চোখ পর্যন্ত বোরখায় ঢেকে স্কুল আসত। রাস্তায় চা বিক্রি করা ছেলেটিকে ওই ন’বছরের মেয়ে চোখ ঢেকে রাখার কারণে দেখতে পায়নি। তার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে বোরখায় চা পড়ে যায়। মেয়ের বোরখায় চা পড়ার কারণে, মেয়েটির অভিভাবক রোকেয়াকে নালিশ করে বলেন, আপনার স্কুলে মেয়ে পাঠাব না। রোকেয়া দুঃখ পেয়েছিলেন ওইটুকু মেয়েকেও পর্দা করতে হচ্ছে দেখে।
ছাত্রীদের স্কুলে নিয়ে আসার জন্য প্রায় এয়ারটাইট বাসের ব্যবস্থা করা হয়, পর্দা রক্ষা করতে হবে বলে। রোকেয়ার এক বন্ধু মিসেস মুখার্জী বাস দেখে বলেছেন, ‘আপনাদের মোটরবাস তো বেশ সুন্দর হইয়াছে! প্রথমে রাস্তায় দেখে আমি মনে করেছি যে, আলমারী যাচ্ছে না কি--চারিদিকে একেবারে বন্ধ, তাই বড় আলমারি বলে ভ্রম হয়! আমার ভাইপো এসে বললে, “ও পিসিমা! সে Moving Black Hole (চলন্ত অন্ধকূপ) যাচ্ছে।” তাই তো ওর ভেতর মেয়েরা বসে কী করে?’ স্কুলের ছোট ছোট মেয়েরা এই অন্ধকূপের মধ্যে ভয় এবং গরমে অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল, বমি করছিল। তাই বাসের দরজার খড়খড়ি নামিয়ে, পর্দা দেওয়া হল। মুসলিম সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি এল রোকেয়ার কাছে, গাড়ির পর্দা বাতাসে উড়ে মেয়েদের বে-পর্দা করছে জানিয়ে। হুমকি এল একই বিষয়ে উর্দু দৈনিকগুলো থেকেও। অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেও তিনি নিজে কিন্তু পর্দা মেনে চলতেন। এ সম্পর্কে রোকেয়া বক্তব্য হল, প্রাণের চেয়ে প্রিয় স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তিনি সমাজের অযৌক্তিক নিয়ম-কাননগুলি পালন করেছেন। ‘অবরোধবাসিনী’র সাতচল্লিশ নং প্রবন্ধে দুঃখ করে তিনি বলেছেন—
“কেন আসিলাম হায়! এ পোড়া সংসারে,
কেন জন্ম লভিলাম পর্দানশীন ঘরে!”
স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখা বা উন্নতির চেষ্টা করার আড়ালে যে তাঁর ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নেই তা জানিয়ে লিখেছিলেন— ‘আপনারা সকলেই জানেন যে এই, এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’টা না থাকলে আমি মরে যাব না। এমনটি নিশ্চয় হবে না যে—
ঘুঘু চরবে আমার বাড়ি,
উনুনে উঠবে না হাঁড়ী,
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ী—
অন্তিম দশায় খাঁবি খাব!
এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই?—চাই, নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়, চাই স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্য নয়; চাই, বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য।’ শিক্ষা তৈরি করে মেরুদণ্ড। শিক্ষা আনে সামাজিক উন্নয়ন। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন রোকেয়া। পিছিয়ে থাকা মুসলিম মেয়েদের প্রথাগত শিক্ষায় গড়ে তোলার জন্য তাই আজীবন লড়াই করেছেন। আর্থিক সংকট দূর করা, ছাত্রী সংখ্যা বাড়ানো সবই প্রায় ছিল তাঁর একক প্রচেষ্টায়।
এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন অনেকের মনে উদয় হতে পারে। একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব, কেন শুধু মুসলমান মেয়েদের কথাই ভাবলেন? এক্ষেত্রে মীরাতুন নাহার যথাযথ যুক্তি দিয়েছেন-- ‘অনেকের ধারণা, রোকেয়া স্বসমাজের অর্থাৎ মুসলমান সমাজের কল্যাণকামী ছিলেন এবং সেই লক্ষ্যেই সমগ্র কর্মপন্থা স্থির করেছিলেন। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। বাস্তববাদিতা তাঁর চরিত্রের একটি অসামান্য গুণ। সেকারণে তিনি আপন কর্মক্ষেত্রকে ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে অগ্রসর শ্রেণীর সঙ্গে একতালে পা মিলিয়ে চলতে সাহায্য করার মানসে অপেক্ষাকৃত ছোট পরিসরযুক্ত করে নিয়েছিলেন। ...হিন্দুর তুলনায় মুসলমান সমাজ সেকাল ও একাল উভয় কালেই অনগ্রসর শ্রেণী। রোকেয়া দেশের সার্বিক উন্নতিকে লক্ষ্য রেখে তাই পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উন্নতিকরণকেই জীবনের লক্ষ্যরূপে বেছে নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের দুর্দশামোচন।’
সাহিত্যিক রোকেয়া
রোকেয়ার সাহিত্যচর্চার মূল বিষয় ছিল সামাজিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আঘাত হানা। শোষিত, বঞ্চিত নারীকে জাগিয়ে তোলা, সমাজ প্রগতির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার চেতনা গড়া। দরদী মনের স্পষ্ট পরিচয় তাঁর রচিত সাহিত্যে পাওয়া যায়। সহজ অথচ ধারালো ভাষা, ব্যঙ্গবিদ্রূপের শক্তির সঙ্গে রঙ্গরসিকতা রোকেয়ার সাহিত্যের বিশেষত্ব।
১৯০২ থেকে ১৯০৭-- এই সময় ‘নবপ্রভা’, ‘মহিলা’, ‘নবনূর’, বিভিন্ন পত্রিকায় সমাজ সচেতনামূলক প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ থেকে ১৯৩২— এই সময় লিখলেন ‘আল এসলাম’, ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’, ‘মাসিক মোহাম্মদী’, ‘নওরোজ’, ‘সওগাত’ প্রভৃতি পত্রিকায়। ‘মতিচুর’ ১ম, (প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ) ও ‘মতিচুর’ ২য় খণ্ড (বিবিধ রচনা সংকলন গ্রন্থ) প্রকাশিত হয় ১৯০৪ ও ১৯২১-এ। ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাস ১৯২৪ (লেখা হয়েছে ১৯০২) এবং ‘অবরোধবাসিনী’ (নকশাধর্মী রচনা গ্রন্থ) ১৯৩১-এ প্রকাশিত হয়।
মানুষের পরিচয় তার শিক্ষাকর্ম, রুচি, চেতনায়। বাহ্যিক সাজসজ্জায় নয়। এই বক্তব্যকে রোকেয়া জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ‘Sultana’s Dream’ বা ‘সুলতানার স্বপ্ন’ কল্প কাহিনিতে। ‘Sultana’s Dream’ ১৯০৫ সালে মাদ্রাজের ‘Indian Ladies Magazine’ প্রকাশিত হয়েছে। ‘সুলতানার স্বপ্ন’ রোকেয়া অনুবাদ করেছেন নিজেই। ‘‘সুলতানার স্বপ্ন’-এ স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে নারীর অবস্থান কী হতে পারে তার ছবি এঁকেছেন। এর কাহিনি একটি কল্পিত নারীস্থানকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত হয়েছে। সুলতানা ভারতবাসী। তিনি ঘটনাচক্রে সেই নারীস্থান দর্শনের সুযোগ পান। ভারতের পর্দানশীন, অবরোধ-বন্দিনী নারী সুলতানা সে দেশে বেমানান। দেশের মহারানী জ্ঞান পিপাসু। দেশের সমস্ত মেয়েদের সুশিক্ষার জন্য নির্মাণ করেছেন অসংখ্য বালিকা বিদ্যালয়। লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজগঠনের দাবি ছিল রোকেয়ার। নারীস্থানের মেয়েদের কর্ম নিপুনতা, স্বাধীন জীবনযাত্রা সেই ভাবনারই রূপায়ন। সেখানকার মহারানী ভারতের সুলতানাকে বলেছেন, ‘যে সকল দেশে রমণীবৃন্দ অন্তঃপুরে থাকে অথবা যে সব দেশে নারী কেবল বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া পুত্তলিকাবৎ জীবন বহন করে—, দেশের কোন কাজ করে না, তাহারা বাণিজ্যের নিমিত্ত নারীস্থানে আসিতে বা আমাদের সহিত কাজ কর্ম করিতে অক্ষম।’ রোকেয়া মনে করেন, মেয়েরা পুতুল জীবন বহন করার জন্য জন্ম গ্রহণ করেনি।
পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আত্মার বিকাশ দরকার। বিজ্ঞানের গবেষণায় স্বামী নিযুক্ত থাকবে আর বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ মাপবে স্ত্রী? ধূমকেতুর গতি বের করবে স্বামী আর পাকশালায় ব্যস্ত থাকবে স্ত্রী? এইরকম অসমসত্ত্ব সমাজ কিছুতেই উন্নতির শিখরে উঠতে পারে না। তাই প্রথমেই প্রয়োজন নারীদের বিজ্ঞান-মনস্কতা। রোকেয়া তাই তাঁর কল্পিত নারীস্থানে ওড়ালেন বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান নারীদের বিজয়-বৈজয়ন্তী। বিজ্ঞানের প্রয়োগে বিনা রক্তপাতে নারীরা সেখানে শত্রুনিধনে সক্ষম, দেশচালনায় পারঙ্গম। ‘Sultana’s Dream’ বা ‘সুলতানার স্বপ্ন’-তে, পুরুষ-নারীর লিঙ্গীয় ভূমিকাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছেন। এই role reversal- এর সুবাদে মেয়েদের বিচরণ বাইরে আর পুরুষেরা রয়েছেন অন্দরে। অফিস সামলানো থেকে দেশ চালানো মেয়েদের দায়িত্বে। এখানে লেখক নারীকে পুরুষের সমান নয়, বরং তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ‘জেনানা’ মহলের বিপরীতে কল্পনা করেছেন ‘মর্দানা’ মহলের। নারীস্থানের একমাত্র ধর্ম প্রেম ও সত্য। অপরাধীকে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয় না। অপরাধীর কঠোর শাস্তি হল দেশ থেকে বিতাড়িত করা। তবে মার্জনাও করা হয়, যদি অপরাধী অনুতাপ প্রকাশ করে। এই চিন্তা সেকালে, এদেশে তো বটেই, সারা বিশ্বেই ছিল অভিনব। সম্পূর্ণ নারীবাদী চিন্তার ফসল তাঁর ‘সুলতানার স্বপ্ন’। রোকেয়ার এই রচনা যুগাতিক্রমী। যুগের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন তিনি। সংকীর্ণ ধর্মচেতনার ঊর্ধ্বে তিনি প্রেম ও সত্যকেই রাষ্ট্রের একমাত্র আচরণীয় ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। সৌরচুল্লি, বিদ্যুৎ, সূর্যকর বা মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জলের ব্যবহার বিষয়ে, অর্থাৎ অফুরান পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বিষয়ে দেশবাসীকে সচেতন করা তাঁর দূরদৃষ্টি বা Vision–কেই আমাদের চিনিয়ে দেয়। তাই আজও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক।’ (চন্দন আঢ্য)
‘পদ্মরাগ’ উপন্যাস লেখা হয়েছে ১৯০২ সালে কিন্তু প্রকাশ হয় ১৯২৪-এ। উপন্যাসের নিবেদন অংশে রোকেয়া তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছ থেকে ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে শোনা একটি গল্প স্মরণ করেছেন, ‘ধর্ম্ম একটি ত্রিতল অট্টালিকার ন্যায়। নীচের তলে অনেক কামরা, হিন্দু-- ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন শাখা; মুসলমান— শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়; ঐরূপ খ্রীষ্টান—রোমান-ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট ইত্যাদি। তাহার উপর দ্বিতলে দেখ, কেবল মুসলমান— সবই মুসলমান; হিন্দু—সবই হিন্দু ইত্যাদি। তাহার উপ ত্রিতলে উঠিয়া দেখ, একটী কক্ষ মাত্র, কামরা বিভাগ নাই, অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু কিছুই নাই— সকলে এক প্রকার মানুষ...’ (‘পদ্মরাগ’, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা।) ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসে রয়েছে দীন তারিণীর গড়া তারিণী ভবনের সক্রিয় কাহিনি। যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে রোকেয়ার জীবন ও আদর্শ। মিসেস এনি বেসান্তের বক্তব্যের সমর্থনে যা রোকেয়া বলেছিলেন— ‘অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী লোক আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ এই আদর্শের অদ্বিতীয় দেশ-- ইহার তুলনা এ ভারত নিজেই। এ দেশে এত স্বতন্ত্র ধর্ম এবং এত পৃথক বিশ্বাসের লোক বাস করে যে, মনে হয় যেন ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম-মত সমূহের প্রদর্শনী ক্ষেত্র। এবং এই দেশই সেই স্থান, যেখানে পরস্পরের একতা, মিত্রতা এবং সহানুভূতির মধ্যে ধর্ম্মের সেই আদর্শ... পাওয়া যাইতে পারে।’ লিঙ্গবৈষম্য ও ধর্মীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে জোরালো সওয়ালের আখ্যান তাঁর ‘পদ্মরাগ’।
‘পদ্মরাগ’ সেই পর্যায়ের উপন্যাস যার পরতে পরতে রয়েছে মানবিকতা, মানবাধিকার, ‘বিবিধের মাঝে মিলন’, শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্য। আমরা প্রথমে ভারতবাসী, তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু— গভীর এই উপলব্ধির জায়গা থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারিণী ভবন। দীনতারিণী দুঃস্থ নারীদের সেবার জন্য প্রথমে তারিণী ভবন গড়ে তোলেন। পরে একটি বিদ্যালয় এবং ‘নারী ক্লেশ নিবারণী সমিতি’ও গঠন করেন। হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান সব ধর্মের, সব বর্ণের, সব শ্রেণির এক ছাদের তলায় বাস। জয়নাব ওরফে সিদ্দিকা বা পদ্মরাগ, সৌদামিনী, হেলেন, সাকিনা, রাফিয়া, নলিনী ওরা সকলেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নির্যাতিত।
উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা ইংরেজ রবিনসনের চক্রান্তে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় তারিণী ভবনে আশ্রয় নিয়েছে। সিদ্দিকা মুসলিম পিতৃতন্ত্রের ছকেও শোষিত। লতিফের সঙ্গে ‘আকদবস্ত’ (রোকেয়া লিখেছেন আকদবস্ত এক প্রকার বিয়ে। তবে পাত্রীর শ্বশুর বাড়ি যাওয়া কিছুদিন স্থগিত থাকে। বাগদত্তা কন্যার মতো।) হয়েছিল সিদ্দিকার। লতিফ ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পড়ে এলে তার চাচার মনে হয়েছিল এই পাত্রের দাম এখন অনেক বেশি পাওয়া উচিত। তাই বিপুল সম্পদশালী খুঁজে অন্য জায়গায় পুনরায় বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। সেই উদ্দেশ্যে সিদ্দিকার দাদা সোলেমানকে একটা প্রস্তাব পাঠায়। সিদ্দিকার ভাগে যে জমি-জায়গা পড়বে সেটা আগে তার নামে লিখে দিলে তবেই লতিফের স্ত্রী হিসেবে সে শ্বশুর বাড়ি প্রবেশের অধিকার পাবে। এমন প্রস্তাব বোন এবং তার পক্ষে অসম্মানের। গভীর এই বোধ থেকে সোলেমান অস্বীকার করেছে সম্পত্তি দিতে। চাচার চাপের মুখে আবার অন্যত্র বিয়ে করেছে লতিফ। কারণ চাচার দানে তাদের পরিবার বেঁচে আছে। সে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে। লতিফের দাদু বেঁচে থাকাকালীন তার পিতা মারা যায়। তাই লতিফরা দাদুর সম্পত্তির অংশীদার হতে পারেনি। শরিয়ত অনুযায়ী তার পিতার ভাগের সম্পত্তির অংশের শরিক হয় তার চাচা। এই চাচার কথা অমান্য করুক তা আত্মীয়রা মেনে নেয়নি। তাছাড়া তাদের আর একটা যুক্তিও ছিল। মুসলিম ছেলের দ্বিতীয় বিয়ে করার অধিকার আছে। এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে সোলেমান সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সিদ্দিকার তালাক করিয়ে নেবে। ঘটনা বিপর্যয়ে লতিফের কাছ থেকে তালাক পায়নি সিদ্দিকা। তাহলে অন্য কোথাও বোনের বিয়ে দিতেও পারবে না। এই অধীনতাকে ভেঙে দেওয়ার চ্যলেঞ্জ জানিয়ে সোলেমান সিদ্দিকাকে পূর্ণাঙ্গ এক মানুষ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু ইংরেজদের চক্রান্তে সোলেমানের মৃত্যু এবং শেষ পর্যন্ত জমিদারি ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে হয় সিদ্দিকাকে। জয়নাব ওরফে সিদ্দিকা ওরফে পদ্মরাগ আশ্রয় পায় তারিণী ভবনে।
রোকেয়া বলেছেন, মেয়েরা যেটা সহজে মানবে না বলে মনে করেছে পিতৃতন্ত্র, তাকে ধর্মের দোহায় দিয়ে মানিয়েছে। বাচ্চাদের যেমন ভূতের ভয় দেখিয়ে শান্ত করা হয় মহিলাদেরও তেমনি ধর্মের অস্ত্রাঘাতে মাথা নত করতে শিখিয়েছে। রোকেয়ার বলিষ্ঠ এই প্রত্যয় থেকেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে অভিযান। যেমন তা সামাজিক আন্দোলনে, তেমন তার প্রতিফলন সাহিত্যেও। ধর্মীয় লিঙ্গবৈষম্য যে সব ধর্মেই রয়েছে, মাঝে মাঝে তারিণী ভবনের মহিলাদের অতীত চারণার মাঝে তাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন রোকেয়া। রাফিয়ার স্বামী ইংল্যন্ড গিয়েছিল ব্যারিস্টারি পড়তে। রাফিয়াও স্বামীর যোগ্য করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য মেম রেখে পড়াশোনা ও গান বাজনা শেখে। সন্তানদের নিয়ে অপেক্ষায় ছিল স্বামীর বিদেশ থেকে ব্যরিস্টারি পড়ে ফেরার। কিন্তু রাফিয়ার স্বামী বিদেশ থেকে মেম বিয়ে করে আনে আর রাফিয়াকে চিঠি মারফত তালাক দেয়। এই অপরাধ দমন করার আইন রাফিয়ার জন্য নেই। স্বামী মেম নিয়ে নির্বিরোধে নতুন সংসার পাতল। নৈরাশ্যে তলিয়ে গিয়ে রাফিয়া গেল পাগল হয়ে। তার স্থান হল তারিণী ভবনে।
জসেফ হোরেসকে বিয়ে করেছিল হেলেন। বিয়ের পর তার ব্যাভিচারের খবর পায়। নর হত্যাকারী জসেফ হোরেস পাগল হয়ে গেলে তাকে ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠায় সরকার। হেলেন ইংল্যান্ড গিয়ে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি দাবি করে আইনের কাছে। কিন্তু এক সময়ের ইংল্যান্ডের আইনেও নারী দাসত্বের বন্ধনে আটকা ছিল। ইংল্যান্ডের আদালত রায় দিল ‘মিসিস্ হেলেন মেরি হরেস্ তাঁহার স্বামী লেফ্টেনান্ট কর্ণেল সিসিল্ জসেফ্ হরেস্ হইতে মুক্তি পাইতে পারে না।’
বাড়িতে ডাকাত পড়েছে দেখে ঊষার স্বামী ঊষাকে ফেলে পালিয়ে যায়। ডাকাতরা ঊষাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে জনৈক ব্যক্তিদের হাতে। ছাড়া পেয়ে ঊষা বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু বাড়ির দরজা ওর কাছে বন্ধ হয়ে যায় চিরতরে। ডাকাতের হাতে পড়ে চরিত্র হারিয়েছে এই মিথ্যে অপবাদে। এই সুযোগে হিতাকাক্ষীর ছদ্মবেশে এক ব্যক্তি কাজ দেওয়ার নাম করে ঊষাকে পতিতালয়ে বেচে দিতে চেষ্টা করে। প্রতিকুল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে ঊষা হয়েছে দীনতারিণী ভবনের প্রধান শিক্ষক। তারিণী ভবন কেল্লাতে জোট বেঁধে এই মেয়েরা সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে,— ‘সমাজের এই সব নালিঘায়ের কি ঔষধ নাই? বাতুলের সহিত চিরজীবন আবদ্ধা থাকিতে হইবে, বিনা কারণে পরিত্যক্তা হইতে হইবে, অপমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী সমভিব্যাহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই হাত পা বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন, স্বামী বাতায়ন উল্লঙ্ঘনে পলায়ন করিলেন বলিয়া স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে,— ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? ... আছে! সে প্রতিকার এই তারিণী ভবনের “নারী-ক্লেশ-নিবারণী-সমিতি”। এর যত পরিত্যক্তা, কাঙ্গালিনী, উপেক্ষিতা, অসহায়া, লাঞ্ছিতা,— সকলে এস তারপর সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা। ...দেখাইতে চাহি যে দেখ, তোমাদের “ঘর করা” ছাড়া আমাদের আরও পথ আছে! স্বামীর “ঘর করাই” নারী জীবনের সার নহে।’
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলিতে— হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম প্রত্যেকের নিয়ম পালনে ভেদ থাকতে পারে কিন্তু বিদ্বেষ নয়। উপন্যাসের নিবেদন অংশে কামরা ভাগের গল্পের মধ্যেই সেই মিলনের বার্তা। কাহিনির ভিতরে সেই মানসিকতার প্রতিফলন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলকে গড়তে চেয়েছিলেন যুক্তি আর মানবিক বোধ দিয়ে। কিন্তু সামাজিক অভ্যাসের প্রতিরোধ তাঁকে পদে পদে বিড়ম্বনায় ফেলেছে। রোকেয়া তারিণী ভবনে তাঁর প্রত্যাশার স্কুলকে এঁকে ছিলেন। তারিণী ভবনের বিদ্যালয়ে ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলিম সব ধর্মের শিক্ষিকা ছিলেন। ‘কি সুন্দর সাম্য!—মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান সকলে যেন এক মাতৃগর্ভজাতা সহদরার ন্যায় মিলিয়া কার্য করিতেছেন।’ তারিণী ভবনে যেমন নানা ধর্মের লোক আছে, তেমন নানা শ্রেণিরও লোক আছে। ভুটিয়া, নেপালি, মাদ্রাজি, কোল, সাঁওতাল, বেহারি প্রভৃতি নানান জায়গার মানুষ তারিণী ভবনে পরিচারিকার কাজ করেন। এই তো প্রকৃত ভারতবর্ষ। যে ভারতকে গড়েছেন দীনতারিণী। দীনতারিণীর হাতে রূপায়িত এটাই রোকেয়ার আদর্শ ভারত। যেখানে সব ধর্ম, সব ভাষা, সব শ্রেণি মিলেমিশে আত্মীয়তার অটুট সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। মানব-প্রেম ভাবনা, অসাম্প্রদায়িক মুক্ত মানসিকতা রোকেয়ার কাজে যেমন ধরা পড়ে তেমন সাহিত্যেও। যার স্পষ্ট ছাপ ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসে।
প্রকৃত ধর্ম চর্চা অর্থাৎ মনুষত্ব্যের জাগরণ, সুনাগরিক এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভর করার দিকেই নজর রেখেছিলেন রোকেয়া তাঁর পাঠক্রম তৈরিতে। পর্বত প্রমাণ বাধা নিয়ে তাঁর সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু দৃঢ় মানসিক জোর নিয়ে সেই স্কুলকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটলে তবেই যে ওরা মুক্তি পাবে। গভীর এই সমাজচেতনা তাঁকে লিপ্ত রেখেছিল নিরলস কর্মে। তাদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাতে চেয়েছিলেন সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেও।
মেয়েদের বুদ্ধি অল্প, সামাজিক এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রামমোহন লিখেছেন, ‘স্ত্রীলোকদের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন যে, তাহাদিগকে অল্প বুদ্ধি কহেন? আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায়ই দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কীরূপে নিশ্চয় করেন?’ রামমোহন যেমন মনে করেছিলেন নারীর সহ্যশক্তির মূলে আছে ধর্মভীতি। রোকেয়াও মনে করেছিলেন ধর্মই মেয়েদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় করেছে। নারী নির্যাতনের মূল কারণ যে অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা এটা বুঝেই রোকেয়া মেয়েদের শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করেছেন। তারিণী ভবনের মেয়েরা নিজের শ্রমের বিনিময়ে খাওয়া-পরা সংগ্রহ করে। কেউ কারো ওপর নির্ভরশীল নয়। আত্মশক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রত্যেকেই নিজ কর্ম ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে যুক্ত হয়েছে। ‘কর্মালয়ে কুমারী, সধবা, বিধবা— সকল শ্রেণির লোকই আছেন। তাঁহারা বিবিধ সূচিকর্ম করেন, চরকা কাটেন, হাতের তাঁতে কাপড় বোনেন, পুস্তক বাঁধাই করেন, নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। কেহ শিক্ষয়িত্রীর পদলাভের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন; কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন; কেহ রোগী-সেবা শিখেন। ফল কথা, এ বিভাগে রমণীগণ আপন আপন জীবিকা স্বয়ং উপার্জন করিয়া থাকেন। ... এতদ্ব্যতীত দেশের অন্যান্য হিতকর কার্য, যথা দুর্ভিক্ষ, বন্যা এবং মহামারী—পীড়িত লোকদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বিভাগ হইতে মহিলাগণ তণ্ডুল, বস্ত্র ও ঔষধ বিতরণ এবং রোগী সেবা করিতে গিয়া থাকেন।’ তারিণী ভবনের মেয়েরা উপার্জন করতে শিখেছে, জনসেবায় যুক্ত থেকে সুনাগরিকের পরিচয় দিয়েছে। সেবা করার সময় মানুষের জাত, ধর্ম, ভাষা পরিচয় তারা খোঁজেনি। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর তাগিদটায় সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে।
মানবসম্পদের উন্নতি না হলে সমাজ ও দেশের উন্নতি হয় না রোকেয়া তা জানতেন। তাই ‘পদ্মরাগ’-এর নারীদের তথা মানুষের উন্নতি ঘটিয়ে দেশের উন্নতি প্রকল্পের অংশীদার করতে চেয়েছেন। তাঁর চেতনার ভারতকে লিঙ্গবৈষম্যহীন, শ্রেণীবৈষম্যহীন, ধর্মীয় বিদ্বেষহীন মানুষের মিলিত সহাবস্থানে দেখতে চেয়েছিলেন। দেশপ্রেমিক রোকেয়ার ‘পদ্মরাগ’-এ তাই মুক্তমনা মানুষদের মিলন। আজকের ভারতবাসীও রোকেয়ার কাঙ্ক্ষিত সেই সহাবস্থানের দিকে তাকিয়ে।
১৯৩১ সালে রোকেয়ার অবরোধ-বাসিনী প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের নিবেদন অংশে তিনি বলেছেন, ‘কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না লইয়া ‘অবরোধ-বাসিনী’ রচিত হইল।’ নিজ জীবনের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকেই অবরোধবাসিনীদের যন্ত্রণা উপলব্ধি করেন রোকেয়া বলেন—‘অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের— বিশেষতঃ আমার কিছুই নাই।’ ‘অবরোধবাসিনী’র প্রবন্ধগুলি সংখ্যার হিসেবে সাতচল্লিশটি। ছোট ছোট ঘটনা অবলম্বনে লেখা। সাত নং প্রবন্ধে এক জমিদার বাড়ির মেয়েরা বিপদেও কীভাবে পর্দা রক্ষা করলেন সেই ঘটনার কথা বলেছেন। চৌকিদার চোরের সাড়া পেয়ে বাড়ির পুরুষদের খবর দেন। পাঁচ/ছয় ভাই কুঠার হাতে ঘরের চারদিকে ঘুরছেন চোর ধরার জন্য। এদিকে চোর সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকেছে। বিবিরা বেগানা পুরুষ দেখে টু শব্দ করেননি। চোর সিন্দুক ভেঙ্গে গয়না, টাকা নিল। পাছে পুরুষ ছুঁয়ে ফেলে। বিবিরা নিজেদের গয়না খুলে দিলেন। নতুন বউ কানের ঝুমকা খুলতে পারছিল না। কান কেটে ঝুমকা নিয়ে চোর বেরিয়ে গেল। বেগানা পুরুষ বেরিয়ে যাবার পর বউরা হাউমাউ শুরু করলেন। এই বিবিদের মতোই ঘটনার কথা বলেছেন নয় সংখ্যক প্রবন্ধেও। কখনও অবরোধ-প্রথার সম্মান রাখতে গিয়ে মেয়েদের প্রাণও দিতে হচ্ছে। তেমন অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন আট নং প্রবন্ধে। তেইশ নং প্রবন্ধে রোকেয়া লিখলেন— ‘অপরের কথা দূরে থাকুক। এখন নিজের কথা কিছু বলি। সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদিগের হইতেও পর্দ্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই; অথচ পর্দ্দা করিতে হইত। পুরুষদের ত অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়ে মানুষের অবাধ গতি— অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ির কোন লোক চক্ষুর ইসারা করিত, আমি যেন প্রাণ-ভয়ে যত্র-তত্র কখনও রান্না ঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরানীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম।’ বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতিতে রোকেয়ার ভাষণ, যেটি ‘সওগাত’ পত্রিকায় ১৩৩৩-এ প্রকাশিত হয়, সেখানে অবরোধের ক্ষতিকারক দিকটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— ‘অবরোধ-প্রথাকে প্রাণঘাতক কার্বন অ্যাসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না! অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।’
মহিলা সমিতি গঠন
নারীর মানবাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে রোকেয়া যেমন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তেমন ১৯১৬ সালে ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’ বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির মূল লক্ষ্যই ছিল মুসলিম মেয়েদের দেশের সুনাগরিক করে গড়ে তোলা। নারী-অধিকার আন্দোলন, আত্মনির্ভরতার শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তায় আস্থা স্থাপন, দরিদ্র মেয়েদের শিক্ষাদান, বস্তিতে বস্তিতে কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রচার, অবরোধ থেকে নারীকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা, নির্যাতিত নারীদের আশ্রয় ও কাজের ব্যবস্থা, এমন নানাবিধ কাজে যুক্ত থেকেছে ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’। এই মহিলা সমিতি গঠনের প্রারম্ভিক পর্বে রোকেয়া সমাজের চোখে হেয় ও হাস্যকর হয়েছিলেন। কিন্তু কোনও বাধা তাঁর অদম্য চেষ্টার অন্তরায় হতে পারেনি। তখন কেউ ভাবতেও পারত না মুসলমান মেয়েরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোবে সভা-সমিতিতে যোগ দিতে। নিজের অধিকার জানান দিতে সোচ্চার হবে। শত উপেক্ষা অগ্রাহ্য করে রোকেয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাঁদের সংগঠিত করেন। তিনি মনে করতেন সমাজের কাজ করতে গেলে গায়ের চামড়া পুরু করতে হয়। যাতে সব গ্লানি, উপেক্ষা-অপমান সহ্য করা যায়। মাথার খুলিকে মজবুত করতে হয়, সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রতিহত করার জন্য। তাই ধর্মদ্রোহিনী বলে সমাজ তাঁকে অবজ্ঞা করলেও তিনি সমিতির কাজ বন্ধ করেননি। বরং প্রবল কৌশলে প্রতিপক্ষকে পরাহত করে অবরোধ বন্দিনীদের বাইরে এনেছেন। বেগম শামসুন নাহার বলেছেন— ‘কোথাও হয়তো বন্দিনী নারী রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু তখনই মনে পড়িয়াছে অভিভাকবকের রোষকষায়িত-লোচন। রোকেয়ার পরামর্শ অনুসারে তখন তিনি সভার নির্দিষ্ট তারিখে কোন নিকট আত্মীয়ের গৃহে যাইতেছেন বলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে পুঁটুলিতে রহিয়াছে সভায় যোগদান করিবার উপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ। এভাবে হতভাগিনীদের শৃঙ্খল কাটিবার চেষ্টায় বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন।’ সভা-সমিতি কাকে বলে সেটাও অনেকে বুঝতেন না। রোকেয়া তাঁদের তৈরি করে নিতেন। ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’-এর কোনও এক সভায় শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের এক মহিলাকে নিয়ে এসেছিলেন রোকেয়া। মিটিং শেষ হয়ে যাওয়ার পর সকলে যখন ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন সেই মহিলা রোকেয়াকে বলেন, সভার নাম করে নিয়ে এলেন কিন্তু সভা তো দেখতে পেলাম না। এইরকম বহু নারীদের নিয়েই মহিলা সমিতির পথ চলা। যাঁদের শেখাতে হয়েছে সভা কাকে বলে, শিক্ষার প্রয়োজন, সামাজিক-সংস্কার, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি, নারী-পুরুষের সম-অধিকারের কথা। রাজনীতি ও সমাজের কাজে আগেই গড়ে উঠেছিল বামাবোধিনী সভা, বামা হিতৈষিণী সভা, আর্য নারী সমাজ, সখী সমিতি। মুসলিম মহিলা সমিতির মঞ্চ থেকে এই মহিলা সমাজের আন্দোলনের সঙ্গে হয়তো রোকেয়া যোগাযোগ রেখেছিলেন। স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করানোর চেষ্টাতেই ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’-এর জন্ম। ‘অনেক অনুদার ও অশিক্ষিত লোক, সমিতির স্বেচ্ছাসেবীদের বস্তীর সীমানা থেকে বিতাড়িত করেছেন, গালমন্দ করেছেন বস্তীর মেয়েদের কুপরামর্শ দিচ্ছে বলে। তবু এঁরা প্রবল আন্তরিকতা নিয়ে বস্তীতে বস্তীতে অবহেলিত নারী ও শিশুর কল্যাণায়োজন করেছেন। আত্মচেতনা বিবর্জিত, নিরক্ষর মুসলিম নারী সমাজের সুপ্ত চেতনার, রোকেয়া অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে এ ভাবেই পৌঁছে দিয়েছেন জাগরণের অভয় মন্ত্র।’ (মহম্মদ শামসুল আলম)। রোকেয়া সাখাওয়াত বিদ্যালয়ের নথি, আঞ্জুমানের কাগজপত্র এবং তাঁর সাহিত্য আলোচনা করলেই বোঝা যায় রোকেয়া আজও কত প্রাসঙ্গিক।
রোকেয়ার ইচ্ছাপূরণ হয়নি। মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হয়নি, নারীস্থানের কল্পনা দিগন্তে কম্পমান। কে মনে রাখে আজ রোকেয়াকে। তবু যেন দেখি রোকেয়া দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের মন, আমাদের বিবেকে, আমাদের চেতনায়। বিস্মরণের ভিতরেও রোকেয়া আজও প্রাসঙ্গিক। আজও তাঁকে প্রয়োজন আমাদের। শতাব্দীর ওপার থেকে রোকেয়ার আশীর্বাদ যেন বর্ষিত হয় আজকের মেয়েদের ওপর। কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রীতিনীতি অনুশাসন মেনে, সেই অনুশাসনকেই নিজেদের অস্তিত্বের একমাত্র পরিচয় যেন তাদের না নিতে হয়। শিক্ষার ঔজ্জ্বল্যে, ভয়হীন মনে, সচেতন আত্মবিশ্বাসে, দীপ্ত, দৃপ্ত প্রতিষ্ঠাতেই তাদের identity আজকের একুশ শতকে দৃঢ়তা পাবে।’ (উত্তরা চক্রবর্তী)। বৈষম্যের বিরুদ্ধে, সমতার প্রশ্নে শুধু আজকের মেয়েদের জন্য নয়, আজকের ভারতবাসীর জন্য রোকেয়া-চর্চা হতে পারে প্রেরণা, উৎসাহ, আশ্রয়।
সহায়ক বই ও পত্রিকা
১। সোনিয়া নিশাত আমিন : ‘বাঙালি নারীর আধুনিকায়ন : ১৮৭৬-১৯৩৯’ (The World of Muslim Women in Colonial Bengal : 1876-1939), অনুবাদ পাপড়ীন নাহার, বাংলা একাডেমী ঢাকা
২। গোলাম মুরশিদ : নারী ধর্ম ইত্যাদি, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা
৩। আনিসুজ্জামান : মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, প্যাপিরাস, ঢাকা
৪। আফরোজা খাতুন : বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা
৫। মুর্শিদাবাদ সৃজনী সাহিত্য পত্রিকা, রোকেয়া স্মরণ সংখ্যা ২০১৯, সম্পাদক-খাদিজা বানু
পুনঃপ্রকাশ । প্রথম প্রকাশ ১১ ডিসেম্বর ২০২০
লেখক : অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক, সমাজকর্মী।
ছবি : সংগৃহীত
1.jpeg)

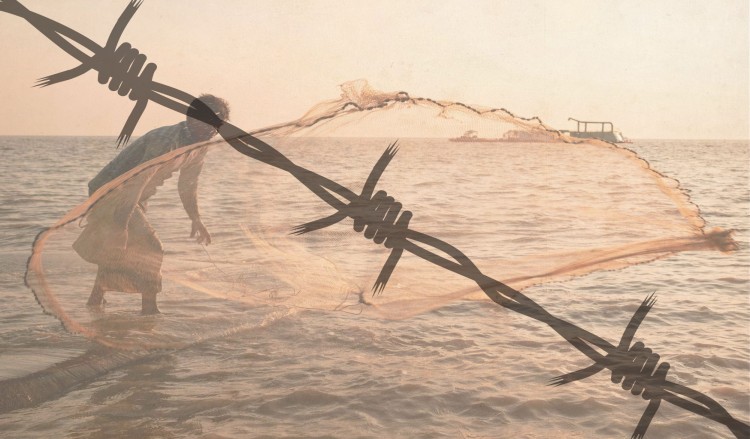


0 Comments
Post Comment