- 26 September, 2023
- 1 Comment(s)
- 9058 view(s)
- লিখেছেন : ড. নন্দিনী জানা
ইংরেজি ১৮৮১ সাল, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ। ভারতের দ্বিতীয় আদমশুমারির রিপোর্ট প্রকাশিত হল। এই রিপোর্টে প্রকাশ বাংলার মোট জনসংখ্যার ছয় শতাংশ (অর্থাৎ, ১০ লাখ বা তার একটু বেশি) ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত, যাঁদের একটি বড়ো অংশ রাঢ়ি এবং বারেন্দ্র শ্রেণির। এই দুই শাখার মধ্যে, বিশেষত রাঢ়ি শ্রেণির মধ্যে প্রচলিত ছিল বহুবিবাহ, যা ‘কৌলীন্য প্রথা’ নামেও পরিচিত ছিল। ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের (১৯৫৫ সালের ২৫ আইন) আগে পর্যন্ত এই বহুবিবাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হয়নি। এই আইনে হিন্দুদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৪ এবং ৪৯৫ এই দুটি ধারার অধীনে আনা হয়েছিল, যাতে এক স্ত্রী অথবা স্বামী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।
কৌলীন্য প্রথার আড়ালে জাতি-ধর্ম রক্ষার নামে বহুবিবাহ ছিল কুলীন ব্রাহ্মণ মেয়েদের কাছে এক দারুণ অবমাননাকর প্রথা। এ থেকে নিষ্কৃতি না পেয়ে বহু বিধবার ও স্বামী পরিত্যক্তার ঠাঁই হয়েছে কাশীতে, নয়তো কলকাতার বেশ্যাপল্লিতে। এই প্রথা বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে বাঙালি ভদ্রলোকদের আবেদন-নিবেদনের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৮৪২ সালেই। কৌলীন্যের করালগ্রাসে মেয়েদের কী যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা হত তা নারীর নিজের জবানিতে প্রথম উঠে এসেছে কুলীন পরিবারে বড়ো হওয়া এবং সেখানেই বৈধব্যে উপনীত হওয়া নিস্তারিণী দেবীর লেখায়। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথা সেকেলে কথা থেকে জানা যায়, কীভাবে বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীন পাত্র হিসাবের খাতায় বিবাহিত বিভিন্ন স্ত্রীদের নাম-ঠিকানা, যৌতুকের পরিমাণ এবং অর্থকরী চাওয়া-পাওয়ার হিসাব রক্ষা করতেন। নিস্তারিণী দেবীর বাবা যদিও দুটির বেশি বিয়ে করেননি, তাঁর ঠাকুরদা ৫৬টি এবং ঠাকুরদার পিতৃদেব ১০৮টি বিয়ে করেছিলেন। এ ছাড়া, তাঁর নিজেরও অন্তত ৪০ জন সতীন ছিলেন। কুলীন বউদের বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ইহজীবনে কোনোদিন স্বামীর ঘর করতে না-পারা বা বিবাহিত মহিলার কোনো রকম অধিকার না-থাকার সঙ্গে সঙ্গে চিরকাল বাপের বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে থেকে দারিদ্রের ও অপমানের জীবন কাটানোই দস্তুর ছিল। অথচ, জাতি মর্যাদা ও সামাজিকতা রক্ষার খাতিরে কুলীনরা এই প্রথাকে টেনে নিয়ে চলতেন। এই ঘৃণ্য সামাজিক প্রথার ফলে কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য যেনতেনপ্রকারেণ বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীন পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাওয়া। এর অন্য দিকটি ছিল এক শ্রেণির পুরুষদের বিয়ের মাধ্যমেই অন্নসংস্থান করা। নিস্তারিণী দেবীর এই বই প্রকাশকালে বহুবিবাহ স্তিমিত হলেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি, তাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা দায়িত্ব নিয়ে বন্ধ করতে দেননি। অথচ, এই প্রথা বন্ধ করার জন্য শিক্ষিত মানুষের সচেতনতা এবং প্রচেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছিল অনেক আগে থেকেই।
ইংরেজি ১৮৭১ সাল, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ। প্রকাশিত হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার বইটি (পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত)। এই বইয়ে বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যে আবারও শাস্ত্রীয় পণ্ডিত এবং রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে বাক্যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন তিনি। তাঁর এই পুস্তকে তিনি রীতিমতো পরিসংখ্যান দিয়ে দেখালেন কৌলীন্য প্রথার আড়ালে কীভাবে সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে ঘৃণিত বহু স্ত্রীগ্রহণ চলছে। একটি তালিকায় তিনি দেখিয়েছিলেন ১৯৭ জন কুলীন পুরুষ ২২৮৮টি বিয়ে করেছে। এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু রক্ষণশীলদের মধ্যে যে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল, তার জবাব দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর রচনা করেন বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক (পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত), যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি ১৮৭২-৭৩ সালে (১২৭৯-৮০ বঙ্গাব্দ)।
তবে, এর অন্তত দেড় দশক আগে থেকেই প্রগতিশীল বাঙালি পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহ-বিরোধী আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল ও প্রস্তাবনাও নেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে সরকারের কাছে প্রথম আবেদনের কৃতিত্ব কিশোরীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের। ১৮৫৫ সালে তাঁদের সংগঠন ‘সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি’-র পক্ষ থেকে বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্বপ্রথম একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়। তারও আগে ১৮৪২ সালে প্রকাশিত বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৮৫৫ সালের শেষ দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ভারত সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠান, যাতে স্বাক্ষর ছিল বর্ধমানের মহারাজের। এরপর একই মর্মে বহু আবেদনপত্র প্রেরিত হলে সরকার নড়েচড়ে বসে এবং ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে একরকম প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয় যে এ বিষয়ে খসড়া বিল তৈরি করা হবে। কিন্তু, রামমোহন-পুত্র রমাপ্রসাদ রায় সরকারের পক্ষে খসড়া বিল তৈরি করলেও সে কপিটি যেমন হারিয়ে যায়, তেমনি সিপাহি বিদ্রোহ নামক প্রবল ঝড়ে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়।
সিপাহি বিদ্রোহের ধাক্কায় দেশীয় শাসনে পরিবর্তন এসেছিল। ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ব্রিটিশ সরকার সরাসরি এই দেশের শাসনভার হাতে তুলে নেয়। তবে, সরকার দেশীয় প্রথা এবং ধর্মীয় আচারে আইনি হস্তক্ষেপের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণের দাবিতে শিক্ষিত সমাজের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল অন্তত ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত। ১৮৬১ সালে এবং ১৮৬৬ সালে বাংলা সরকারের কাছে বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আবারও আবেদন পত্র পাঠান দেশীয় ভদ্রলোকরা। শুধু তাই নয়, ১৮৬৬ সালের আবেদনপত্র পাঠানোর পর ওই বছরের ১৯ মার্চ বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর সিসিল বিডনের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে আলাদাভাবে ডেপুটেশন দেন কলকাতা শহরের গণ্যমান্য বেশ কিছু ব্যক্তি, যাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগরও। লেফটেন্যান্ট গভর্নর তাঁদের বহুবিবাহ-বিরোধী বিল আনা এবং আইনি হস্তক্ষেপের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। এরপর, বাংলার সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারকে আইনি হস্তক্ষেপের বিষয় অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখার সময় জানানো হয়েছিল যে কৌলীন্য প্রথার কারণে প্রধানত বাংলাতেই বহুবিবাহের দৌরাত্ম্য জারি আছে। ১৮৬৬ সালের ৮ আগস্ট লেখা এই চিঠির উত্তরে ভারত সরকার তাঁদের মতামত স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দেন যে, ভারত সরকার মনে করেন না যে বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসাধারণ, এমনকি শিক্ষিত মানুষদের একাংশও রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ সমর্থন করেন, কারণ এই প্রথা হল একটি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। সরকারি বিরূপতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরও তাঁর গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে জনমত তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, সরকার তাঁদের মতামত জানানো সত্ত্বেও এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধানের জন্য এবং শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটি সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি নিয়োগ করেন যার অন্যতম সদস্য ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। দেশীয় সদস্যদের মধ্যে একমাত্র তিনিই আইন করে এই প্রথা বন্ধ করার জন্য কমিটির রিপোর্টে জোরালো সওয়াল করেছিলেন এবং সরকারও অনুভব করেছিলেন যে আইনি হস্তক্ষেপ ছাড়া গতি নেই। কিন্তু বাকি সদস্যরা তাঁদের অনুসন্ধানের পর যে মত ব্যক্ত করেছিলেন — অর্থাৎ, সাধারণ ভাবে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু পুরুষদের মধ্যে একাধিক বিয়ে করার রীতি কমে যাওয়া এবং আইনি হস্তক্ষেপ না করা — তাকে মেনে নিয়েছিল বাংলা সরকারও। আধুনিক শিক্ষা ও উন্নত সমাজচিন্তার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে এই প্রথা একদিন নির্মূল হবে এই আশাতেই শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক তাঁদের এ বিষয়ে উদ্যোগে ইতি টেনেছিলেন। পরিতাপের বিষয় হল, এই প্রথায় সবচেয়ে ক্ষতবিক্ষত যে মেয়েরা তাঁদের মত নেওয়া হয়নি এবং সে সময় এ কথা কেউ ভাবেনওনি।
বহুবিবাহ নিয়ে ভদ্রলোকদের এই উদ্যোগের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চেও। ১৮৫৩ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক প্রকাশ ও সফল ভাবে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পর থেকে পরবর্তী দশ-পনেরো বছরে অনেকগুলি নাটকে কৌলীন্য প্রথার ফলে সৃষ্ট বহুবিবাহ এবং সপত্নী সমস্যা নিয়ে বাংলা স্টেজ আলোড়িত হয়েছিল। এই নাটকগুলিতে কুলীনদের ‘বিবাহ-ব্যবসায়ী’ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল। টাকাপয়সার জন্য শ্বশুরবাড়িতে তাদের অন্যায় অত্যাচার, অভব্য আচরণ এবং কুলীন স্ত্রীর যন্ত্রণা ও হেনস্থার ছবি ফুটে উঠেছিল সে সময়ের অজস্র বাংলা নাটকে। নাট্যকাররা কৌলীন্যপ্রথা অর্থহীন এবং বিয়ের ব্যাপারে পাত্রের ব্যক্তিগত গুণাবলীই বিবেচ্য এই ধরণের সমাধানও তুলে ধরেছিলেন। বহুবিবাহ নিয়ে সমাজ সংস্কারকদের আন্দোলন ও সরকারের কাছে তা বন্ধ করার জন্য আবেদন পাঠানোর সময়কালে এই বিষয়ক নাটকের সংখ্যাধিক্য ঘটেছিল। তবে ১৮৭১ সালে যখন বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার বিষয়ে জনমত গঠনের জন্য বই প্রকাশ করছেন এবং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার মতো রক্ষণশীল সংগঠন বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছে, সে সময়ও এই নাটকগুলির রচনা ও প্রকাশ তুঙ্গে পৌঁছেছিল। কিন্তু, ১৮৭৪ সালের পর এই ধরনের নাটক রচনায় ভাটা পড়ে।
প্রথমে ইংরেজি শিক্ষিত সংস্কারপন্থী ভদ্রলোকেরা এই আন্দোলন শুরু করলেও পরবর্তীতে হিন্দু রক্ষণশীলদের একাংশও বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা সরকারি হস্তক্ষেপে এ বিষয়ে আইন বা বিধি প্রণয়নের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ১৮৬০-এর দশক থেকেই বাংলায় ধীরে ধীরে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এ ক্ষেত্রে ১৮৬৭ সালে প্রবর্তিত হিন্দু মেলা একটি অনুঘটকের কাজ করেছিল। এই মেলা যার আদত নাম ছিল চৈত্র মেলা, তার উদ্দেশ্য ছিল জনচিত্তে স্বদেশানুরাগ জাগিয়ে তোলা। এর দ্বিতীয় অধিবেশনেই মেলার সম্পাদক তাঁর বক্তৃতায় জানান, “এই মেলার উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা”। প্রথম থেকে মেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত স্বদেশানুরাগী মনোমোহন বসু ১৮৭৩ সালে ‘হিন্দু আচার ব্যবহার — সামাজিক’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই মনোমোহন বসুই বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনের একজন নেতা হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৬৬ সালের পর জনমত গঠন করতে গিয়ে এবং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার আন্দোলনের সমর্থন আদায় করতে বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ-বিষয়ক লেখাটিতে একদিকে শাস্ত্রীয় আলোচনা করে দেখান যে বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় এবং অমানবিক। অন্যদিকে, এই প্রথা বন্ধ করার জন্য তিনি রাজবিধি বা আইনের সাহায্যের জন্য সওয়াল করেন। এতে হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ বেশ কিছু পণ্ডিত যেমন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, রাজকুমার ন্যায়রত্ন, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, সত্যব্রত সামশ্রমী এবং গঙ্গাধর কবিরাজ কবিরত্ন অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং তাঁর পুস্তকটির বিরোধিতা করে কলম ধরেন। এর ফলে শাস্ত্রীয় তর্ক জোরদার হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, যাঁরা যুক্ত ছিলেন সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গেও, তাঁরা ছিলেন বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থক। কিন্তু, তাঁরা কোনোভাবেই বহুবিবাহ সংক্রান্ত বিদ্যাসাগরী মতের সঙ্গে সহমর্মিতা পোষণ করেননি। সোমপ্রকাশ ১২৭৮ বঙ্গাব্দে বিশেষত সরকারি আইনের বিরোধিতা করে প্রস্তাব রাখল যে, “যাবৎ ইঁহারা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া সমাজসংস্কার করিতে না পারিতেছেন, তাবৎ কালের নিমিত্ত আমরা একটি সদুপায় বলি […] এই বলিয়া গবর্নমেন্টে আবেদন করুন, শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি কারণ ব্যতিরেকে যাঁহারা একাধিক বিবাহ করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক বিবাহে ৫০০ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে।” অর্থাৎ, পরিহাসের বিষয় হল একাধিক বিয়ের জন্য সরকার কর আদায় করবে, তাতে দেশীয় হিন্দুদের স্বাজাত্যবোধে আঘাত লাগবে না। বিদ্যাসাগর সোমপ্রকাশ-এ এর প্রত্যুত্তরে লেখেন যে সরকারকে কর দিলেও তা সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হবে এবং দরিদ্র কুলীনদের ওপর অত্যাচার হবে; তা ছাড়া এই ধরনের হস্তক্ষেপের তুলনায় সব সময়েই আইন করে এই কুৎসিত প্রথা বন্ধ করা বেশি যুক্তিযুক্ত। তারানাথ তর্কবাচস্পতিও ওই সোমপ্রকাশ পত্রিকাতেই লিখলেন, “তিনি বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে যেরূপ শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন […] বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। […] শিক্ষার প্রভাবে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে। অতএব তজ্জন্য আইনের আবশ্যকতা নাই।” স্বাদেশিকতার বোধের দ্বারা দেশীয় ঐতিহ্য এবং প্রাচীন ধর্মকে জাতির মধ্যে ঐক্য সৃজনের জন্য তুলে ধরা হল, অথচ একটি প্রচলিত সংস্কার ঘৃণ্য এবং বর্জনীয় জেনেও তাকে ছেঁটে ফেলার জন্য কোনো আইনি পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করা হল। তার একমাত্র কারণ ছিল তাহলে বিদেশি শাসক দেশের ধর্মীয় প্রথা বা লোকাচারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেয়ে যাবে।
শুধু তাই নয়, নিন্দুকদের জবাব দেওয়ার জন্য যখন ১৮৭৩ সালে বিদ্যাসাগর রচনা করলেন বহুবিবাহ সংক্রান্ত তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবনা, তখন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে যেভাবে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন তাও অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁর সমালোচক পণ্ডিতদের শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিদ্যাসাগর, এমনকি কোথাও কোথাও তাঁর ভাষা শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছিল তাও সত্যি। কিন্তু বঙ্কিম শুধু সে কথা লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, ‘বহুবিবাহ’ নামক তাঁর সেই প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে ধরা দিল ব্যঙ্গ। বিদ্যাসাগর কৌলীন্য প্রথার সংখ্যাধিক্য বিষয়ে যে তথ্য দিয়েছিলেন তার যথার্থতার প্রতি কটাক্ষ করে লেখা শুরু করে বঙ্কিম বহুবিবাহ শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় এই তর্কে না গিয়ে সোজাসুজি শাস্ত্রসিদ্ধ প্রথা মেনে চললে আরও কত কত অনিষ্টকারী নিয়ম মানতে হবে তার প্রতি বিদ্রুপ করেন, কারণ বিদ্যাসাগর বলেছিলেন শাস্ত্র মানলে বহুবিবাহ করা উচিত নয়। এ ছাড়া, বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের জন্য আইনি হস্তক্ষেপের প্রশ্নে কেন শুধু হিন্দু কুলীন ঘরের মেয়েদের কথা বলেছেন, মুসলমানদের বহুবিবাহ বন্ধ করার কথা বলেননি — এমন বেশ কিছু কূট প্রশ্ন তুলে বিদ্যাসাগরের যুক্তিগুলিকে লঘু করে দেওয়ার চেষ্টাও করলেন। বঙ্কিম ব্যঙ্গ করে লিখলেন, “আমরা এমত বলিতেছি না যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্মশাস্ত্রে স্বয়ং বিশ্বাসবিহীন বা ভক্তিশূন্য। […] কেবল আমাদিগের কপালদোষে বহুবিবাহ নিবারণের সদুপায় কি, তৎ সম্বন্ধে তিনি কিছু ভ্রান্ত।” এই প্রথা যে বর্জনীয়, এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিন্দুমাত্র সন্দেহ যেমন ছিল না, তেমনি সুশিক্ষার প্রসার হলে যে এই প্রথার শীঘ্রই অবসান হবে এই বিশ্বাসেও তিনি ছিলেন অটল। শেষ পর্যন্ত এই মতেরই জয় হয় এবং সরকারি আইন দ্বারা বহুবিবাহ রদ করার প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সঠিক ভাবেই বুঝেছিলেন যে শাস্ত্র নয়, আসলে লোকাচার বিধৃত থাকে সামাজিক রীতির মধ্যে। ফলে এই সামাজিক রেওয়াজ অমান্য করে কুলীনদের সংকীর্ণ একটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ হওয়ার যে রীতি ছিল তাকে ভেঙে পাত্র-পাত্রী আদান প্রদান করা গেলেই আস্তে আস্তে এই প্রথার নিবারণ হবে।
১৮৭১ সালের পর পূর্ববঙ্গে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রাচীন সমাজের ইংরেজি-না-জানা ব্যক্তির একক প্রচেষ্টা এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। সত্যি সত্যিই শিক্ষা এবং মানসিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কুলীন স্বামীর বহু স্ত্রী গ্রহণ করার প্রথা ভবিষ্যতে একদিন বন্ধ হল, কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করার সময়ে যত তাড়াতাড়ি এটি বন্ধ হবে ভেবেছিলেন, তত শীঘ্র কিন্তু এ প্রথা নির্মূল হয়নি। বিস্ময়কর যে, পুরোনো প্রথা বর্জনীয় এবং নারীর প্রতি চরম অবমাননাকর জেনেও তাকে সমূলে উৎপাটন করার সহজ পথ থাকতে তা অবলম্বন করা হল না এবং তা কোনো একদিন তিরোহিত হবে ভেবে ভবিষ্যতের আশায় কুলীন কন্যাদের জলাঞ্জলি দেওয়া হল শুধু দেশাচার রক্ষা করার নামে। অর্থাৎ, ১৮২৯ সালে সতীদাহ করাকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করতে যে ইঙ্গ-ভারতীয় আইন ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়েছিল, ১৮৬৬ সালের পর দেশীয় মানুষের জীবনে সেই আইনের হস্তক্ষেপকে অনধিকার চর্চা মনে করতে শুরু করেছিলেন হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এবং তাঁদের প্রভাবে জনগণের একটি বড় অংশ।
হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের এই ভাবপ্রবণতা যে কোন্ দিকে নিয়ে যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৮৯১ সালের সহবাস সম্মতি আইন। এই আইন সংক্রান্ত বিলে সহবাসের বয়স ১০ বছর থেকে সামান্য বাড়িয়ে মাত্র ১২ বছর করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। হিন্দুদের গর্ভাধান ব্যবস্থা এতে মানা যাবে না এই যুক্তিতে এই বিল যাতে পাশ না হয় সেই লক্ষ্যে প্রবল আন্দোলন শুরু হয় হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের নেতৃত্বে। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে বার্ধক্য এবং অসুখে জর্জরিত বিদ্যাসাগরের কাছে সহবাস সম্মতি আইনের বিল সম্বন্ধে মত চাওয়া হলে তিনি এই বিলের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর এই আচরণের সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু এ কথা মনে উদয় হয় বই-কি যে সারাজীবন অনেক বিরুদ্ধস্রোতে লড়াই করতে করতে জীবনের শেষে এসে তিনি কি উপলব্ধি করেছিলেন যে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত নব্য যুবকেরা আর যুক্তি দিয়ে সামাজিক কুপ্রথার ব্যাখ্যা খুঁজছে না, বরং ঐতিহ্যের নামে তাকে টিঁকিয়ে রাখাকেই প্রগতি মনে করছে, এমনকি তাতে ধর্ম ও সামাজিক আচারের নামে মেয়েরা যতই বলিপ্রদত্ত হোক না কেন? সে কারণেই নিস্তারিণী দেবীর সেকেলে কথা আজও এত মূল্যবান। বইটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে জাতীয়তাবাদী নেতারা যাই মনে করুন না কেন, বর্জনীয় সামাজিক প্রথা অত সহজে বর্জিত হয় না। ধর্ম ও জাতি রক্ষার নামে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোরদার হয় এবং বলিপ্রদত্ত হয়ে চলে মেয়েরাই। পরিশেষে মনে রাখা যাক যে, ধুতি-চাদর পরিহিত ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের অন্যতম জীবনীকার বিহারীলাল সরকার ছকভাঙা এই মানুষটির ধর্ম ও শাস্ত্রের প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াইকে সহজে মেনে নিতে না পেরে লিখেছিলেন, “দয়াময় কৃপা করিয়া, কালধর্মসিদ্ধির মানসে তাঁহার হৃদয়ে পরদুঃখকাতরতার স্রোত এতই প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন যে, বংশপরম্পরাগত ধর্মভাব ও শাস্ত্রজ্ঞান কোথায় ভাসিয়া গেল! বিধবার দুঃখ দেখিয়া বিদ্যাসাগর গলিয়া গেলেন। বহুবিবাহে কুলীনকামিনীর ক্লেশ দেখিয়া তদ্বিমোচনে বিদেশী রাজার আশ্রয় লইলেন। […] তাঁহার সেই দয়াগুণে তাঁহার পৈত্রিক ধর্ম, শাস্ত্রশ্রদ্ধা সবই ভাসিয়া গেল।”
পুনঃপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ১ নভেম্বর ২০২০
লেখক : অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক
ছবি : ইন্টারনেট


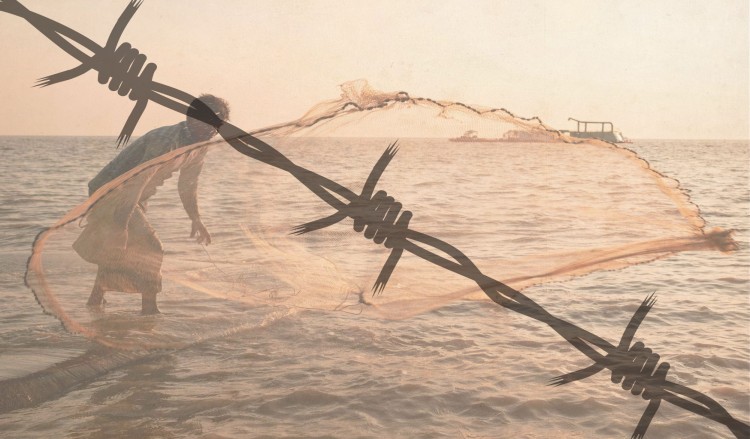


1 Comments
ভালো লেখা
26 September, 2021
ভালো লেখা।
Post Comment