- 23 April, 2025
- 0 Comment(s)
- 386 view(s)
- লিখেছেন : অমর্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
।। উপসংহার ।।
রানীকে যে হোমে রাখা হয়েছিল, নিয়তির এক অবাক বৃত্তীয় চলনে কুড়ুনি আর পুঁটিও কেমন করে জানি বন্দিদশা থেকে পালিয়ে সেই হোমে গিয়েই আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হয়। সরকারি হোম না আদৌ অন্য কিছু, সেসব তাদের জানা ছিল না। কেবল ঘর্মাক্ত, রক্তাক্ত অবস্থায় ছুটতে ছুটতে তারা যখন অনেক রাত্তিরে সেই হোমের সামনেটায় এসে পড়েছিল, হোমের ইনচার্জ ভদ্রমহিলাও তখন কী কারণে জানি দরজার সামনে একলাটিই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি অবশ্য লক্ষ্য করেননি কুড়ুনিদের পিছনে আরও কিছু লোক সন্তর্পণে ধাওয়া করে এসেছে। কুড়ুনিদের সরকারি হোমে ঢুকতে দেখে অবশ্য তারাও আর অনুসরণ করেনি। কিন্তু খবর পৌঁছেছিল অন্যদের কাছেও। একই সময়ে বাথরুম যাওয়ার প্রয়োজনে রানীকেও নীচে নামতে হয়। সাত বছর পর কুড়ুনিকে দেখেও তাকে চিনতে রানীর এতটুকুও অসুবিধে হয়নি।
সেই রাত্তিরেই সুখেনের ফোনে কুড়ুনির খবর পৌঁছয়। এরপর মালতীর সম্মতিতেই অম্বরীশ-সুতনু-লক্ষণ-সত্যেন প্রমুখের কারসাজিতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পাচার চক্রের বিষয়টি অন্তর্তদন্তমূলক রিপোর্টাজ সিরিজ হিসেবে ডেইলি রিভিউতে প্রকাশিত হয়। তিন পর্বে সাজানো সেই বিস্তারিত রিপোর্টে মালতী, সুখেন এবং সুখেনের বাবা সনাতনের বেশ কিছু লিখে যাওয়া বয়ান-সহ রাজনীতিগত ভাবে লক্ষণ মজুমদারের বিরোধী আরও কিছুজনের মৌখিক সাক্ষ্য উল্লিখিত হয়। সোনালী সামন্ত সবরকম সহায়তা করেন। এরপর মালতীর জামিন মঞ্জুর হতেও আর বেশি সময় লাগে না। রাতারাতি কলকাতার সাংবাদিক জগতে সুবর্ণ নিজেও এক পরিচিত মুখ হয়ে ওঠে। কেবল অনেক পরে সুবর্ণ জানতে পারে, ডেইলি রিভিউয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী বিনিয়োগ করে থাকে, অম্বরীশ মিত্রের কোম্পানিকে ছাপিয়ে গোপনে তারাই সেইসময় রাজ্যের শাসক দলেরও অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিল। তাই অম্বরীশ মিত্রের রাজনৈতিক কেরিয়রেরও পতন শেষমেশ অবশ্যম্ভাবী ছিল বোধহয়।
বেশ কয়েক মাস পেরিয়েছে। দীর্ঘ শীতকালের পর বৈশাখ এখন। চৈত্রশেষের কয়েকদিনের দাবদাহ কাটিয়ে হঠাৎ গতকাল আর আজ শহরে বৃষ্টি হয়েছে খুব। অথচ দুপুরের পর থেকে বৃষ্টি কাটিয়ে আবারও নরম রোদ। হাওয়ায় কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা ভাব। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে সুবর্ণ। মালতী এখন কোনও এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কর্মী। মাঝেমাঝে তার সঙ্গে সুবর্ণের দেখা হয়। অপর দিকে সত্যেন বাদে আর সব ক’জনেরই জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। যদিও প্রতি সপ্তাহে থানায় গিয়ে তাদের হাজিরা দিতে হয়। সে আর কতটুকু বিষয়। মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুবর্ণ সেন। নেহাত সত্যেনের হয়ে জামিন দাঁড়ানোর মতো ছিল না কেউ। নচেৎ তারও জামিন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মনটা উদাস লাগছে। সুবর্ণ উবের বাইক নেয়। বকুল নতুন ক্লাসে উঠেছে। এখনও বরুণের পুলকারেই তার যাতায়াত। চন্দনের ক্লাবে যাওয়ার বিষয়েও তারপর থেকে আর একদিনও ব্যাঘাত ঘটেনি। এই সম্পর্কের শীতলতাও সুবর্ণের কাছে কোনও নতুন বিষয় নয়। সে ওটিপি বলে দেয়। বাইক ছুটতে শুরু করে। একেকটা উড়ালপুল পেরিয়ে যায়। সাদার্ন এ্যাভিনিউ, রোয়িং ক্লাব, রবীন্দ্র সরোবর ফ্লাইওভার।
শরৎ বোস রোড আর সাদার্ন এ্যাভিনিউ যেখানে মিশেছে, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের খুব কাছেই, সেই মোড়ে পৌঁছে উবের থেকে নেমে পড়ল সুবর্ণ। এই চত্বর তার ভারী পরিচিত। বহুদিনের শুষ্কতার পর বৃষ্টি নেমেছিল। তাই হাওয়াতে সে এখনও ভেজা ঘাসের গন্ধ পায়। আকাশে এখনও গোধূলি-রোদ। হাঁটতে হাঁটতে রোয়িং ক্লাবের পাশ দিয়ে সে সরোবরের ব্রিজটার উপর এসে দাঁড়ায়। এই জায়গাটা থেকে চারপাশে অনেকটা আকাশ দেখা যায়। অনেক নীচে রবীন্দ্র সরোবর রেলস্টেশন। ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম। এখন ট্রেনের সময় নয়। সুবর্ণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। সে জানে শহর কলকাতার পেটের ভিতর এখনও যে কয়েকটি জায়গায় কিছুটা হলেও শূন্যতা, নিস্তব্ধতার আভাস মেলে, দক্ষিণ-শহরের এই রবীন্দ্র সরোবর চত্বর – এবং আরও বেশি করে তার আশেপাশেকার এই ফ্লাইওভার ও তার সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তাগুলি, সেগুলির মধ্যে অন্যতম। তার কলেজ জীবন মনে পড়ছিল। গত কয়েক মাসে সে নতুন করে পৃথিবীকে দেখেছে। মালতীর কেসটা নিয়ে হইচই শুরু হওয়ার পর মুম্বাই থেকে ফোন পেয়েছিল সুবর্ণ। জাতীয় স্তরের কোনও এক সংবাদ প্রতিষ্ঠান তাদের বার্ষিক পুরষ্কারের জন্য সুবর্ণকে নির্বাচন করে। মুম্বই থেকে আরও একটা ফোন এসেছিল। অনেকদিন পর সুবর্ণের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন সুস্মিতাশ্রী পন্নিরসেলভম। তিনি নিজেও নাকি নানা কারণে, অনেকের সঙ্গে একত্রে যুঝতে গিয়ে পরিকল্পিত এ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয়ে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। তবু গলার জোর কমেনি তাঁর। তাঁর কাছ থেকেই সুবর্ণ সুরেশ মানসুখানির নতুন কেলেঙ্কারির বিষয়ে জানতে পারে। জানতে পারে বোম্মাই-পূর্ণিমা বলে দুজন দলিত কৃষিজীবী মানুষের বিষয়েও। সুস্মিতাশ্রী আক্ষেপ করেন, বোম্মাইরা হাল ছেড়ে দিয়ে এই ভারতবর্ষের জনারণ্যে হারিয়ে গিয়েছে। সুবর্ণ উপলব্ধি করে বিরাট এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই করা কার্যত অসম্ভব।
সে উড়ালপুলের দেওয়ালে ঝুঁকে দাঁড়ায়। সিমেন্টের থাম, নীল-সাদা রঙ। আকাশে একটা মিষ্টি আলো ছড়িয়ে পড়েছে। হাওয়ার গন্ধটাও তার ভালো লাগে। দুটো-একটা গাড়ি ছুটে চলে যায়। ওপাশ থেকে একজন বেলুনওলা উঠে আসছে। তার হাতে লম্বা বাঁশের আগায় রঙবেরঙের বেলুন-সম্ভার। রঙিন কাগজের ঘুরন্ত চাকতি। সুবর্ণের কিনতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে কেনে না। তার মনে পড়ছে মুম্বই শহর। মেরিন ড্রাইভের লম্বা বিকেল। তখনও সুবর্ণের বিয়ে হয়নি। চন্দন মুম্বইতে এসেছিল একবার। চন্দনের সঙ্গে সুবর্ণের প্রেম কলেজ-জীবনের শেষ থেকেই। তখনও চন্দন এভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি। তখনও চন্দন হোসে মার্তির কবিতা আওড়ায়। মেরিন ড্রাইভের উপর আশ্লেষে সুবর্ণকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে। সুবর্ণ সমস্ত শরীর দিয়ে সেই গন্ধ পায়। আদতে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন এক ঘেরাটোপ-বিশেষ। সেই পাক থেকে কারোর এতটুকুও রক্ষে নেই। এই অজগরের বিরুদ্ধে কারোর একার লড়াই চলে না। চললেও সে লড়াইয়ের সাফল্য স্বল্পমেয়াদী খুব।
পুঁজি আর বাজারের এই বিরাট কৃষ্ণগহ্বরের অতলতার হদিস কারোর মগজে থাকে না। সবাই কেবল স্রোতের অনুকূলে, অথবা বিপরীতে কয়েকজন, সাঁতার কাটতে চায়। তবু সে অন্ধকার স্রোত, আজ অথবা কাল, একদিন সবাইকেই গিলে ফেলবে ঠিক। সুবর্ণ চোখ বুজে চন্দনকে অনুভব করে। এই গোধূলি-বিকেলের একাকীত্বে আজ, সে অনেকক্ষণ ধরে চন্দনকে অনুভব করে। সমস্ত শরীরের উষ্ণতায়। সন্ধ্যায় সে বাড়ি ফিরবে। সারা গায়ে তার চন্দনের গন্ধ লেগে থাকবে। কেবল খাটের ওপাশের মানুষটি এতটুকুও সুঘ্রাণ পাবে না তার।
[***]
রাখী শ্রীবাস্তব হুমায়ুন’স টুম্বের সামনে এসে দাঁড়ায়। জায়গাটা কতখানি পালটে গিয়েছে। কিউআর কোড সম্বলিত টিকিট হাতে নিয়ে, সে মাটির নীচের প্রবেশপথ দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে এসে হুমায়ুন চত্বরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ডানদিকে তাকালেই ইশা খানের সমাধি। একটু এগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সেই চত্বরে নামতে হয়। এই চত্বর ছেড়ে আরও একটু সামনে এগোলেই আরবি সরাই। পথের শেষে হুমায়ুন’স টুম্ব। প্রাচীন সেই সৌধের বিশালতা এবং তারই সঙ্গে গোলাপী বেলেপাথরের গায়ে আরও রকমারি সব অন্য পাথরের অদ্ভুৎ সুন্দর কারুকাজ, রাখীকে চিরকাল মুগ্ধতায় ডুবিয়ে এসেছে। এখানে আসতে তার ভালো লাগে। আজ বাহারের কথা খুব মনে পড়ছে তার। হঠাৎই পিছন থেকে কেউ তার কাঁধ স্পর্শ করে। “রাখী শ্রীবাস্তব বলে মনে হচ্ছে?” সে ফিরে তাকায়। “কল্যাণ! তুই!” রাখী অবাক হয়ে লোকটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।
কল্যাণ মুখার্জি। অনেক বছর আগে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাখী যখন গণজ্ঞাপন বিষয়ে স্নাতকোত্তরের শেষ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন সেই একই সময়ে তার সঙ্গে আলাপ হয় কল্যাণের। জেএনইউয়ের অর্থনীতি বিভাগের পিএইচডি। সে তখন সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কোর্সওয়ার্কের কাজ শুরু করেছে। জেএনইউ থেকেই কল্যাণের স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা। পাশাপাশি জেএনইউ ক্যাম্পাসে বাম ছাত্র-রাজনীতিরও সক্রিয় সংগঠক। রাখী, বাহার দুজনের সঙ্গেই কল্যাণ পরিচিত হয়ে ওঠে। আর ছিল অনন্যা। কল্যাণের সবসময়ের বান্ধবী, সহচর অনন্যা নায়ার। রাখী নিজেই তড়বড় করে জিজ্ঞেস করে, “একা এসেছিস? অনন্যা কোথায়?” কল্যাণ মৃদু হাসে। “আছে, আছে। সবাই আছে। ওদিকে ঘাসের উপর বসে একটু বিশ্রাম করছে ওরা দুজন।” “দুজন?” রাখী অবাক হয়, “আরেকজন কে?” কল্যাণ হেসেই চলেছে, “বাবা হওয়ার খবরটা তোকে দেওয়া হয়নি বোধহয়,” রাখী ঠিক কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। মাঝে এতগুলো বছর! চ্যাপলিন ঠিকই বলেছিলেন। প্রযুক্তি আমাদের কাছাকাছি এনেছে ঠিকই, কিন্তু আমরাই ক্রমশ নিজেদের মুখ আরোই নিজেদের দিকে ফিরিয়েছি। গ্লোবাল ভিলেজে আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী হলেও, আদতে আমরা কারোরই কোনও খবর রাখি না। সে প্রায় পুরনো দিনের মতোই হালকা গালাগালি দিয়ে উঠতে চায়, “চল, চল। আলাপ করাবি চল – বাহার থাকলে,” সে চুপ করে যায় হঠাৎ।
কল্যাণ রাখীর হাত স্পর্শ করে। “জানি।”
সে হাত ছুঁয়ে থাকে, “খবরের কাগজে আমরা দেখেছি সবকিছুই।” রাখীর অস্ফূটে বলে, “আমাদের কাগজটা বন্ধ হয়ে গেল কল্যাণ। আমরা চালাতে পারলাম না।” কল্যাণ আগ বাড়িয়ে কোনও সান্ত্বনা দেয় না। কেবল হাত ছুঁয়ে থাকে। অনেক পরে সে বলে ওঠে, “আমাকেও ওরা দেশে থাকতে দিল না জানিস।” রাখী কল্যাণের দিকে তাকায়।
“ওর ভালো নাম সূর্যেন্দু। ডাকনাম পাপাই।” হুইলচেয়ারে শোয়ানো ছেলেটার সঙ্গে কল্যাণ রাখীকে আলাপ করিয়ে দেয়। রাখী কিছু বলতে পারে না।
ছেলেটা যে কোনওদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে পারবে না – এসব কিছু ভাবার আগেই পাশ থেকে অনন্যা ওর কাঁধে হাত রাখে। “এই রাখী, আমাদের পাপাই কিন্তু খুব গান শুনতে ভালোবাসে জানিস তো? ফোক সংস, বাংলা গান, তোর মনে আছে সেসব?” রাখীর কাছে সবকিছুই আবছায়া, অন্ধকার হয়ে আসতে চায়। শেখর খাণ্ডেলওয়াল যে গ্রুপে ছিলেন, সেই গ্রুপেই কাজ করত কল্যাণ। কিন্তু গত বেশ কিছু মাস যাবৎ সমস্ত অফিসেই এক চরম দমবন্ধকর অবস্থা। এক অদ্ভুৎ অন্ধকার। কল্যাণ চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। বিদেশের কোনও এক গবেষণা সংস্থায় নতুন চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে তার।
“সত্যি কথাটাই যদি লিখতে না পারি, মানুষের কাছে যদি সঠিক বিশ্লেষণটাই পৌঁছতে না পারি – তাহলে আমার নিজের কাছে, মানুষ হিসেবে আর আমার কতটুকু দাম পড়ে থাকে বল?” কল্যাণ রাখীকে জিজ্ঞেস করে।
“কিন্তু, পাপাই, অনন্যা?” রাখী জিজ্ঞেস করে, “ওদেরকেও তো নিয়ে যেতে হবে?”
কল্যাণ সরাসরি জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, “দেখি। আগে আমি নিজে গিয়ে একটু গুছিয়ে নিই সবকিছু। ওদেশে থাকলে হয়তো পাপাইও আরেকটু,” কল্যাণ আনমনে আবারও চুপ করে যায়। অনন্যা রাখীর হাত ধরে আছে, “এই, তুই কী এত ভাবছিস বল তো? চল। আজ তোকে খাটাই একটু। একা আমরা দুজনে হুইলচেয়ারটা রোজ ওই টুম্বের উপর টেনে তুলতে পারি না। আজ তুই আছিস। চল পাপাইকে নিয়ে আমরা উপর থেকে ঘুরে আসব আজ।” কল্যাণ কপট রাগে অনন্যার দিকে তাকায়, “অমনি, মানে শ্রমিকপন্থী দেখলেই কি তোর মালিকের মতো খাটাতে ইচ্ছে করে?” “উফফ, থামবি তোরা?” রাখী যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। “চল, চল। উপরে না গেলে মজা কোথায়?”
ওরা চারজন খাড়াই পাথরের সিঁড়ি বেয়ে হুমায়ুন সৌধের উপরে উঠে আসে। “জানিস,” অনন্যা রাখীর হাত ধরে বলে ওঠে, “এই এখানেই কিন্তু দারাশুকোরও সমাধি। কেবল কেউ জানে না কোন সমাধিফলকটি তার।” “দারাকে এখানেই কবর দেওয়া হয়েছিল?” রাখী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে। “আলবাত,” পাশ থেকে বলে ওঠে কল্যাণ, “সম্রাটের বিরাগভাজন হওয়ার কারণে দারার চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। হাতির পিঠের উপর তার দেহকে চাপিয়ে ছিন্নভিন্ন করে সারা শহর ঘোরানো হয়েছিল। মৃতদেহের গায়ে নোংরা ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। তবু শেষ অবধি তো সম্রাটেরই নিজ-পরিবারের লোক। তাই রাজকীয় এই সমাধিস্থলেই দারাকে কবর দেওয়া হয়। কেবল ফলকে কোনও নাম লেখা হয় না। বিভিন্ন সময় অনেকে নানা সম্ভাবনার কথা বললেও, আজ অবধি কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেনি বিরাট এই সমাধিক্ষেত্রে, ঠিক কোন ফলকটির তলায় শাহজাদা শুয়ে আছেন।”
রাখী মৃদু হাসে। “কেই বা তাঁকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল উপনিষদ অনুবাদ করতে? কেই বা তাঁকে বেদান্ত আর সুফির তুলনাত্মক চর্চার আলোকে লিখতে বলেছিল মাজমা-উল-বাহরেঁ, অথবা দ্য মিংলিং অব টু ওশানস!” কল্যাণ রাখীর দিকে তাকায়।
“আদতে এই পৃথিবীতে কারোরই অবদান হারিয়ে যাওয়ার নয়। তাৎক্ষণিক ভাবে অনেকে গ্রহণযোগ্যতা না পেলেও, অন্তিমে ঠিকই তাঁদের পরিশ্রম স্বীকৃতি লাভ করবে। আর সমসময়ে দাঁড়িয়ে এঁরা প্রত্যেকেই মানুষকে আরও একটু ভালো রাখার চেষ্টা করে যাবেন।” অস্ফূটে অনন্যা বলে ওঠে, “এই, অনেক গম্ভীর কথাবার্তা হয়েছে,” সে রাখী আর কল্যাণকে তাড়া দেয়, “একটু গান হোক দেখি এবার। রাখী, তোর সেই বাংলা গানগুলো মনে আছে এখনও? তাহলে ওই গানটা হোক না,” সে কল্যাণের দিকে তাকায়, “ওই যে, যেটা শুনতে আজকাল পাপাইয়েরও ভালো লাগে ভীষণ!” ওদের প্রত্যেকেরই চোখ যেন চকচক করে ওঠে। নরম বিকেলের রোদ। কল্যাণ গান গাইতে শুরু করেছে।
ওরা গলা মেলায়।
হুইলচেয়ারের উপর কাত হয়ে নেমে থাকা মাথাটা অল্প দুলছে। সে এক অদ্ভুৎ মায়াবী আলোর বিকেল। গোলাপী বেলেপাথরের দেওয়াল আর রঙচঙে পাথরের চকমকি কাজ। বিরাট সেই সৌধের নীরবতায় এক আশ্চর্য সুর ভেসে যেতে থাকে। রাখী কেবল অস্ফূটে উচ্চারণ করে, “রবীন্দ্রনাথ।”
ভালোবাসি, ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি॥
আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় ভাসি॥
সেই সুরে সাগরকূলে বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন-হাসি॥
(সমাপ্ত)
আগের পর্বের ঠিকানা – https://nariswattwo.com/welcome/singlepost/the-siege-serialised-novelette-series-twenty-two-


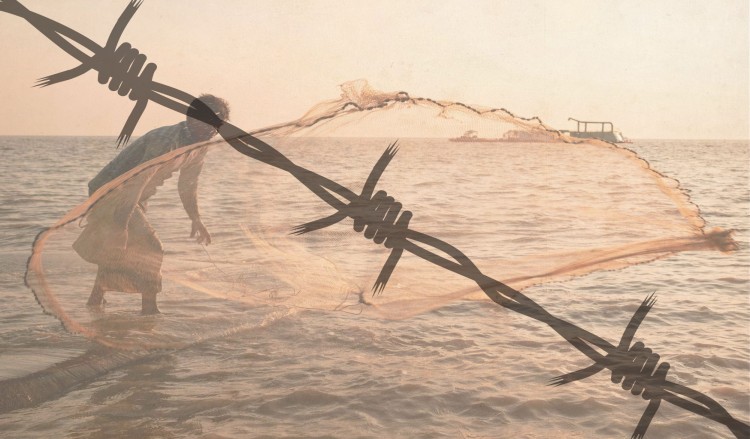


0 Comments
Post Comment